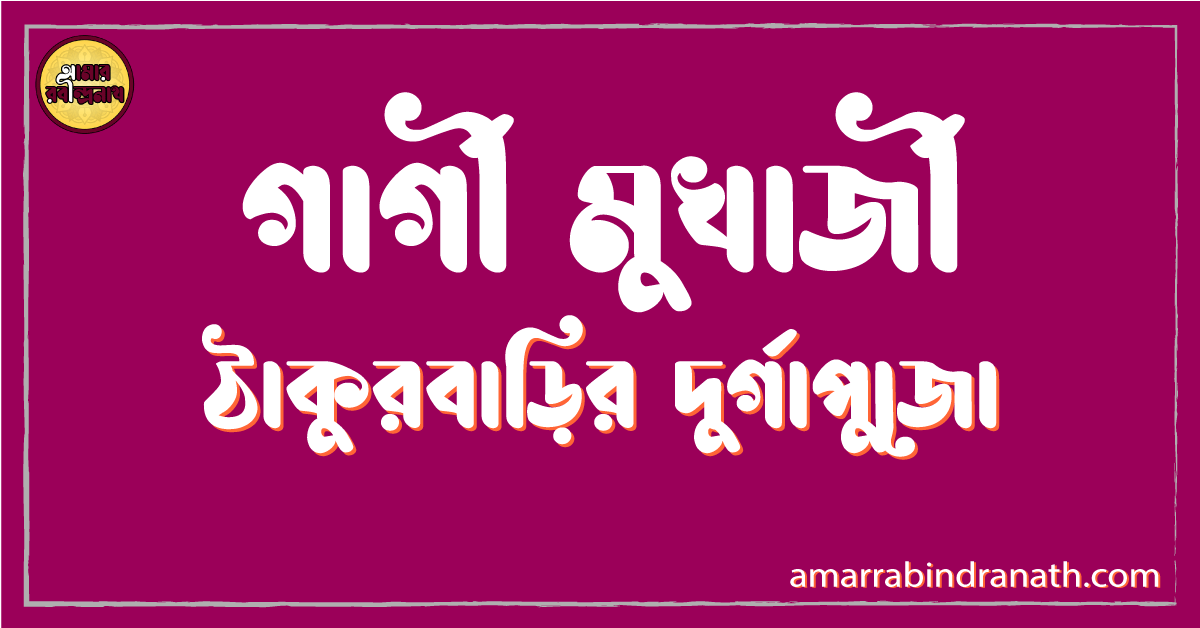রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বা বা ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজো নিয়ে প্রচুর গল্প রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে অনেক লেখালেখিও হয়েছে। সেই সব লেখনীর মধ্য থেকে আমরা কিছু নির্বাচিত লেখা উঠিয়ে দিলাম।
ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজো – গার্গী মুখার্জী
ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজো : সপ্তদশ শতাব্দী শেষ দিকে পঞ্চানন কুশারী তার কাকা শুকদেব কে নিয়ে যশোর থেকে এলেন কলকাতার গঙ্গার তীরবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামে। এই পঞ্চানন কুশারী হলেন ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস সিদ্ধ আদি পুরুষ।
[ ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজো ]
পঞ্চানন কুশারী ছিলেন বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। কলকাতায় এসে বসতি স্থাপন করলেন জেলেপাড়ায়। এই পাড়ায় ইতিপূর্বে কোন ব্রাহ্মণ ছিল না, এখানে পঞ্চানন পরিচিত হলেন ঠাকুরমশাই হিসেবে। (তবে পঞ্চানন জীবিকা নিয়ে দ্বিমত আছে, কেউ বলে তিনি জাহাজওয়ালাদের মাল সরবরাহ করতেন, কেউ বলে পুজো অর্চনাই ছিল তাঁর জীবিকা)। এপাড়ার লোকেদের মুখে পঞ্চানন কুশারী হলেন পঞ্চানন ঠাকুর। ইংরেজরা ও তাকে ঠাকুর বলেই ডাকতেন, শুধু উচ্চারণ বিকৃত হয়ে তা দাঁড়ালো টেগর। এরপর কুশারী পদবি উঠে গেল, তাঁরা নিজেরাও ঠাকুর পদবী ব্যবহার করতেন।
১৭০৭ সালে রাফেল সেলডন কলকাতার প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হলে কোম্পানির উপর নিজ প্রভাব খাটালেন পঞ্চানন।
সেলডন, পঞ্চাননের দুই পুত্র জয়রাম ও সন্তোষরাম কে বহাল করলেন আমিন পদে। এরপর জরিপ, জমিজমা কেনাবেচা, গৃহ নির্মাণে দালালি করে দুজনেই বেশ পয়সা কামালেন। ধর্মতলা অঞ্চলে নিজস্ব বসতবাড়ি তুললেন জয়রাম।
জয়রামের চার ছেলে মধ্যে নীলমণি ১৯৬৫ সালে উড়িষ্যায় কালেক্টর হন এবং দর্পনারায়ন কলকাতায় বসেই নানা উপায়ে অর্থ উপার্জন করে ধনী হয়ে উঠলেন। দুই ভাইয়ের মিলে পাথুরিয়াঘাটায় নির্মাণ করলেন বিরাট বসতবাড়ি।
নীলমণি ঠাকুর ও দর্পনারায়ন ঠাকুরের মধ্যে তাদের সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ বাধলে নীলমণি ঠাকুর বংশের লক্ষ্মী জনার্দন ও শালগ্রাম শিলা নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয় এবং পরে কলকাতার মেছুয়া বাজারে অর্থাৎ চিতপুরের কাছে, যা আজকের জোড়াসাঁকো নামে পরিচিত সেই অঞ্চলে এক বিশাল বাড়ি নির্মাণ করেন। সেই বাড়িই পরবর্তীতে ঠাকুরবাড়ি বলে পরিচিত হয়।
নীলমণি ঠাকুর সূচনা করলেও ঠাকুর বাড়ির পুজোয় রাজকীয় জাঁকজমক আসে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকেই। দ্বারকানাথ নিজেই দেবদ্বিজের ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রতিদিন পূজা করতেন, হোম করতেন। দুজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত পুজোর ভোগ দেওয়া ও আরতির কাজ করতেন।
দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইংরেজদের সাথে যোগাযোগ ছিলই। ইংরেজ সাহেব -মেমরা যখন বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন, তখন তাদের খাওয়া-দাওয়ার তদারকি দূর থেকে সারলেও তাদের সাথে খাবার গ্রহণ করতেন না তিনি। বরং খাওয়া দাওয়া শেষ হলে তিনি পোশাক পাল্টে গঙ্গা জল ঢেলে শুদ্ধ হতেন। পরবর্তীতে ব্যবসার খাতির যখন বেড়ে গেল, তখন তিনি আর ছুতমার্গ ধরে রাখতে পারলেন না। ইংরেজদের সঙ্গে খাবার গ্রহণে বসলেন বটে, তবে তিনি তখন থেকে আর মন্দিরে ঢুকতে না।
১৮ জন ব্রাহ্মণ পুজোর সব দায়িত্ব পালন করতেন। পুজোর সময় তিনি দূর থেকে প্রণাম সারতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মা অলকাসুন্দরী দেবী ছিলেন ধর্মপ্রাণা। ইংরেজ ম্লেচ্ছদের সঙ্গে দ্বারকানাথের এই মেলামেশা তার পছন্দ ছিল না, যদিও তিনি ব্যবসার খাতিরে নিয়ম নিষেধে কিছুটা শিথিলতা দেখিয়েছিলেন, কিন্তু দ্বারকানাথের স্ত্রী দিগম্বরী দেবী ছিলেন এ বিষয়ে শাশুড়ি অলকাসুন্দরীর থেকেও কঠোর। তবে জানা যায় তিনি ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। কথিত আছে দ্বারকানাথের আমলে ঠাকুরবাড়ির দুর্গা প্রতিমার মুখ দিগম্বরী দেবীর মুখের আদলে তৈরি করা হতো।
দ্বারকানাথের আমলে দুর্গা পুজোতে রাজকীয় আয়োজন হতো। যে কোন বনেদি বা জমিদার পরিবারের পূজাকে টেক্কা দিতে পারতো ঠাকুরবাড়ির পুজো। পরিবারের সদস্যদের নতুন জামা কাপড় উপহার দেওয়া হতো, ছেলেমেয়েরা পেত দামী দামী পোশাক। যেমন ছেলেদের চাপকান, জরি দেওয়া টুপি, রেশমি রুমাল ইত্যাদি । আসত আতরওয়ালা, জুতোর মাপ নিতে আসত চিনাম্যান, মহিলাদের শাড়ি নিয়ে আসত তাঁতিনীরা। মহিলারা পড়ত নীলাম্বরী, গঙ্গাযমুনা ইত্যাদি শাড়ি।দিনে মহিলারা পড়ত সোনার গহনা আর রাতে জরোয়া। বাড়ির মেয়েরা দ্বারকানাথ ঠাকুর এর কাছে, সুগন্ধির শিশির এবং মাথার সোনার বা রুপোর ফুল উপহার পেতেন আর ছোটরাও পেত শিশি করে আতর। বাড়ির ভৃত্য, কর্মচারী সকলেই পেত নতুন জামা কাপড়।
বিশাল ঠাকুরদালানে হত পুজোর আয়োজন। উল্টো রথের দিন গঙ্গার পাড় থেকে আনা হত প্রতিভা গড়ার মাটি। কাঠামো পুজো হলে তবেই কাঠামোতে মাটির প্রলেপ পড়ত, দিনের পর দিন প্রলেপ চড়িয়ে প্রতিমা তৈরি হতো, কিন্তু সে কাজ হতো সম্পূর্ন পর্দার আড়ালে।
এখানকার প্রতিমার বৈশিষ্ট্য ছিল এক চালা-অর্ধচন্দ্রাকৃতি মূর্তি। পুজোর দিনগুলোতে দিনে দুবার বেনারসি বদলানো হতো দুর্গার। কখনো বেনারসি ছেড়ে দুর্গাকে পড়ানো হতো তসর অথবা গরদ। মাথার মুকুট থেকে কোমরের চন্দ্রহার সমস্ত গহনা পড়ানো হতো সোনার। এমনকি দ্বারকানাথের নির্দেশ অনুযায়ী দশমীর বিসর্জনের সময় সেইসব বহুমূল্যবান গহনা খোলা হতো না।
ঠাকুর বাড়ির দুর্গাপুজোতে ভোগ ছিল দেখবার মতো। অন্নভোগ হত মিষ্টান্ন সহযোগে ৫১ পদের। সঙ্গে থাকত বিভিন্ন ফল ও ডাবের জল। দর্শনার্থীদের মধ্যে পুজো শেষে সেই ভোগ বিতরণ করা হতো। দশমীতে ঠাকুর বিসর্জনের পর ঠাকুরবাড়িতে হত বিজয়া সম্মিলনী। তখনকার বিশিষ্টজনেরা ঠাকুরবাড়ির এই উৎসবে আমন্ত্রণ পেতেন। আমন্ত্রণ পত্র লেখা হতো দ্বারকানাথ ঠাকুরের পিতা রাম ঠাকুরের নামে।
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ঠাকুমা অলকাসুন্দরী দেবীর কাছেই মানুষ, তাই তিনি কখনো কখনো মালা গেঁথে দিতেন শালগ্রাম শিলার জন্য, কালীঘাটে পুজো দিতে যেতেন, নিত্য সূর্য প্রণাম করতেন। কিন্তু যুবক দেবেন্দ্রনাথ যখন রাজা রামমোহনের সান্নিধ্যে এলেন, পৌত্তলিকতা বিরোধী হয়ে উঠলেন, তখন তিনি সংকল্প করলেন:
“কোন প্রতিমা কে পূজা করিব না, কোন প্রতিমাকে প্রণাম করিব না, পৌত্তলিক পূজার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না”।
1839 সালে দেবেন্দ্রনাথের বয়স বাইশ বছর, সে বছর ঠাকুর বাড়িতে পুজো হলেও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুজোর সঙ্গে সমস্ত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেন। সে বছর তিনি কখনও পুকুরের ধারে একা বসে এবং তখনও তত্ত্ববোধিনী সভায় একেশ্বরবাদী আলোচনায় সময় কাটালেও পরবর্তীকালে পুজোর সময় তিনি কলকাতা ছেড়ে দেশ পর্যটনে বেড়িয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি ঠাকুরবাড়ির চিরাচরিত পুজো উঠিয়ে দিতে পারেননি।
রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মাদর্শেই বিশ্বাসী ছিলেন, তার মূর্তি বা প্রতিমা পুজোর প্রতি কোন বিশ্বাস ছিল না কোনোকালেই। তিনি উপনিষদের মনের মানুষের সন্ধান করেছেন সারা জীবনকাল। তবে বাঙ্গালীদের জীবনে, সামাজিকতায়, মানসিকতায় দুর্গোৎসব যে সুখের স্পর্শ, যে আনন্দ ধারা বয়ে এনে দেয় তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন। এই উৎসব যে বাঙ্গালীদের মিলনক্ষেত্র তা তিনি মন থেকেই মেনেছেন। তাইতো লিখেছেন,” বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বৃথা সময় নষ্ট কিন্তু সমস্ত দেশের লোকে যাতে মনে করে একটা ভাবের আন্দোলন একটা বৃহৎ উচ্ছ্বাস এনে দেয় সে জিনিসটা কখনোই নিষ্ফল এবং সামান্য নয়”।
জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পুজো বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে নানান মতভেদ আছে, কেউ বলেন ১৮৫৭ সালে কেউবা ১৮৫৮ সালে তো কেউ বলেন ১৮৭৫ সালে এই পুজো বন্ধ হয়। তবে সত্যিটা হল ১৮৫৮ সাল থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পুজো চলে যায় শরিকদের হাতে, ক্রমে বন্ধ হয়ে যায় ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজো।
লেখিকা পরিচিতি
গার্গী মুখার্জী, রবীন্দ্রমেলার সদস্যা।
ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপূজা – অমিত গোস্বামী
যশোর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন পঞ্চানন কুশারী। ব্রাহ্মণ হলেও কুলীন নন। কিছুটা পতিত। কাজেই তাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে হলো সুতানুটি অঞ্চলে গঙ্গার ঘাটে ব্যবসায়ীদের পূজা করা। আর সে কারণেই লোকে তাঁকে ঠাকুরমশাই বলে ডাকতে শুরু করল। ক্রমে তিনি পঞ্চানন কুশারীর থেকেও পঞ্চানন ঠাকুর নামেই বেশি পরিচিত হয়ে উঠলেন। এই পঞ্চানন ও তার পরবর্তী প্রজন্ম এই শহরে বেশ কিছু সম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠেন।
একটা সময় পঞ্চানন ঠাকুরের দুই নাতি নীলমণি ঠাকুর এবং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের মধ্যে সেই বিষয়সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ বাধল। যার জেরে নীলমণি ঠাকুর বংশের গৃহদেবতা লক্ষ্মী এবং শালগ্রাম শিলা নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতার মেছুয়াবাজার অর্থাৎ আজকের জোড়াসাঁকো অঞ্চলে এক সুবিশাল বাড়ি নির্মাণ করেন। এই নীলমণি ঠাকুর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পত্তন যেমন করেছিলেন সেইসঙ্গে তিনি ঠাকুর পরিবারে দুর্গাপূজারও সূচনা করেছিলেন। সালটা ১৭৮৪। তবে ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপূজা রাজকীয় আকার ধারণ করেছিল নীলমণি ঠাকুরের নাতি প্রিন্স দ্বারকানাথের হাত ধরেই।
দ্বারকানাথ ঠাকুরের দেবদ্বিজে ভক্তিতে অটুট ছিলেন। তিনি নিজে প্রতিদিন পূজা করতেন এবং হোম দিতেন। দুজন ব্রাহ্মণ ছিল বটেÑ তবে তারা শুধুমাত্র পূজার ভোগ দিতেন আর আরতি দিতেন। ইংরেজদের সঙ্গে দ্বারকানাথের যোগাযোগ ছিল। তার বাড়িতে সাহেব-মেমদের নিমন্ত্রণ হতো। তিনি তাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু খেতে বসতেন না। দূরে দাঁড়িয়ে তদারকি করতেন। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে তিনি কাপড়-চোপড় পাল্টে ফেলতেন। গঙ্গাজল ঢেলে শুদ্ধ হতেন। পরে ব্যবসায়ের খাতিরে তিনি যখন আরো ঘনিষ্ঠ হলেন ইংরেজদের সঙ্গে তখন তিনি এই ছুৎমার্গটি ধরে রাখতে পারলেন না। তাদের সঙ্গে খেতে বসতে হলো। তখন তিনি আর মন্দিরে ঢুকতেন না।
১৮ জন ব্রাহ্মণ পূজার সব দায়িত্ব পালন করতেন। আর পূজার সময় দূর থেকে তিনি প্রণাম করতেন। দ্বারকানাথের মা অলকানন্দা ছিলেন খুব ধর্মশীলা। তিনি ছিলেন মৃতবৎসা। দ্বারকানাথকে দত্তক নিয়েছিলেন। সন্ন্যাসীদের প্রতিও তাঁর বিশ্বাস ছিল। দ্বারকানাথের ম্লেচ্ছ ইংরেজদের সঙ্গে ওঠা-বসা অলকাসুন্দরী পছন্দ করতেন না। কিন্তু ব্যবসায়ের কারণে এই মেলামেশাকে বাধা দিতেন। তাদের সঙ্গে একটুআধটু মদও খেতে দ্বারকাকে অনুমতি দিতেন। কিন্তু গোমাংস খাওয়ার ব্যাপারে একেবারে না। দ্বারকানাথের স্ত্রী দিগম্বরী দেবী ছিলেন তাঁর শাশুড়ি অলকাসুন্দরীর চেয়েও কঠোর। তিনি নিজে খুব ভোরে উঠতেন।
এক লাখ হরিনামের মালা ছিল তার। এটার অর্ধেক জপে খেতে বসতেন। তারপর বাকিটা শেষ করতেন। লক্ষ্মীনারায়ণের নিয়মিত সেবা করতেন। বাড়িতে ইংরেজরা আসা-যাওয়া করলেও তিনি তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হননি। তাঁর স্বামী মদ-মাংস ও ম্লেচ্ছসঙ্গ পছন্দ আরম্ভ করলে তিনি স্বামী সঙ্গও ছেড়ে দেন। দূর থেকে তার সেবাযত্নাদির তদারকি করতেন। কখনো স্বামীর ছোঁয়া লাগলে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে নিতেন। ধর্মের কারণে দ্বারকানাথ ও তার স্ত্রী দিগম্বরীর সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল ঝামেলাপূর্ণ।
এই দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় দুর্গাপূজার আয়োজন ও আড়ম্বর যেমন রাজকীয় ছিল পূজায় পরিবারের সদস্যদের জন্য নতুন জামাকাপড় ও উপহারের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন খুব দরাজ।
ছেলেমেয়েদের প্রতি বছর পূজায় দামি দামি পোশাক উপহার দিতেন। ছেলেদের জন্য প্রতি বছর বরাদ্দ ছিল চাপকান, জরি দেয়া টুপি আর রেশমি রুমাল। জুতোর মাপ নিয়ে যেত চিনাম্যান। আসতেন আতরওয়ালাও। তাঁর কাছে ছোটরা পেত এক শিশি করে আতর। বাড়ির মহিলা মহলে আসতেন তাঁতিনীরা। তারা নিয়ে আসতেন নীলাম্বরী, গঙ্গাযমুনাÑ এমন কত রকমের শাড়ি। পূজার ক’দিন মহিলারা দিনে পরতেন সোনার গয়না, রাতে জড়োয়া।
দ্বারকানাথের কাছ থেকে প্রত্যেক পূজাতেই ঠাকুরবাড়ির মেয়ে-বউ উপহার পেতেন এক শিশি দামি সুগন্ধী, খোঁপায় দেয়ার সোনা বা রুপোর ফুল, কাচের চুড়ি আর নতুন বই। প্রিন্স দ্বারকানাথ পার্বণী দেয়ার ব্যাপারে খুব দরাজ ছিলেন। বাড়ির দুর্গাপূজায় আত্মীয়স্বজন, ভৃত্য-কর্মচারীরাও তাঁর কাছ থেকে পেতেন নতুন জামাকাপড় ও উপহার।
সেকালের কলকাতার যে কোনো জমিদার বা বনেদি পরিবারের দুর্গাপূজাকে টেক্কা দিতে পারত ঠাকুর পরিবারের পূজা। বিশাল বাড়ির প্রকাণ্ড খোলা ঠাকুরদালানে হতো মাতৃ আরাধনার আয়োজন। উল্টোরথের দিন ঠাকুরবাড়ির প্রতিমা গড়ার মাটি আসত গঙ্গার পাড় থেকে। কাঠামো পূজা সারা হলে সেই কাঠামোয় মাটির প্রলেপ পড়ত। মূর্তি শিল্পী সমস্ত নিয়ম মেনে শুদ্ধাচেরে প্রলেপের পর প্রলেপ চড়িয়ে দেবী দুর্গার অবয়ব ফুটিয়ে তুলতেন।
প্রকাণ্ড ঠাকুরদালানে প্রতিমা নির্মাণের কাজ হতো পর্দার আড়ালে। ঠাকুরবাড়ির দেবী দুর্গার বৈশিষ্ট্য ছিল অর্ধচন্দ্রাকৃতির একচালার মূর্তি। তবে বিশেষ গুরুত্ব পেত প্রতিমার মুখের আদল। প্রিন্স দ্বারকানাথের স্ত্রী দিগম্বরী দেবী ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী এক নারী, কথিত আছে তাঁর আমলে ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপূজার মূর্তি দিগম্বরী দেবীর মুখের আদলে তৈরি করা হতো। কেবলমাত্র দেবীর মুখাবয়ব নয়, পূজার দিনগুলোতে মূর্তিকে দুবেলা বেনারসি শাড়ি বদল করে পরানো হতো, আবার কখনো পরানো হতো দামি তসর কিংবা গরদের শাড়ি।
প্রতিমায় পরানো হতো প্রচুর সোনার গয়না, মাথায় সোনার মুকুট থেকে কোমরে চন্দ্রহারÑ সবই প্রতিমার গায়ে শোভা পেত। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপূজার ভোগও ছিল বলার মতো। এবেলা-ওবেলা দুবেলাই অন্ন থেকে মিষ্টান্ন সব মিলিয়ে একান্ন রকমের পদ দুর্গার ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হতো। সঙ্গে থাকত নানা রকমের ফল, ডাবের জল প্রভৃতি। সেগুলো পরে ঠাকুরবাড়ির পূজার দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা হতো।
রাজকীয় বৈভবে ঠাকুরবাড়ির পূজা শেষ হতো নবমীর রাতে। পরের দিন দশমীতে প্রতিমা বিসর্জন। গঙ্গায় ঠাকুরবাড়ির প্রতিমা বিসর্জনও হতো মহাধুমধাম করে। প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা ছিল নজরকাড়া। শোভাযাত্রায় ঢাকি ছাড়াও থাকতেন নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রী, তাঁদের পাশাপাশি গ্যাসবাতি নিয়ে পথ চলতেন বেশ কয়েকজন। ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরবাসিনীরাও বিসর্জনে যেতেন গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত, তাঁরা যেতেন দরজা বন্ধ করা পাল্কিতে। কথিত আছে ঠাকুরবাড়ির প্রতিবেশী শিবকৃষ্ণ দায়ের বাড়িতে প্রতিমার গায়ে শোভা পেত বহুমূল্য ফরমায়েশি গয়না।
যদিও সে গয়না ভাসানের আগেই খুলে নেয়া হতো। তবু এতে দ্বারকানাথ ভাবলেন তাঁর আয়োজনে কোথাও যেন একটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। তাই মনে মনে ঠিক করলেন, এর যোগ্য জবাব দেবেন। তিনিও প্যারিস থেকে বহুমূল্য ফরমায়েশি গয়না আনিয়ে তা প্রতিমাকে পরালেন। আর আভিজাত্যের লড়াইটা জিততে দ্বারকানাথের নির্দেশে সেই সব বহুমূল্য গয়না সমেতই দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন দেয়া হয়েছিল।
প্রতিমা ভাসানের পর ঠাকুরবাড়িতেও স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে হতো বিজয়া সম্মিলনী। সেই উপলক্ষে খোলা ঠাকুর দালানে হতো জলসা। নাচ, গান, নাটক এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ চলত মহাসমারোহে। সেকালের নামকরা ওস্তাদরা তাঁদের গানে মাত করে দিতেন আমন্ত্রিত অতিথিদের। ঝাড়বাতির নিচে চলত বিজয়ার রাজসিক খাওয়াদাওয়া, মিষ্টিমুখ, গোলাপজল, আতর, পান আর কোলাকুলি।
তখনকার সমাজের বিশিষ্টজনরা ঠাকুরবাড়ির দুর্গোৎসবে আমন্ত্রণ পেতেন। আমন্ত্রণপত্র লেখা হতো দ্বারকানাথের পিতা রামমণি ঠাকুরের নামে। উল্লেখ্য, ১৮৩৮ সালে ১২ বছরের বালক দেবেন্দ্রনাথ তাঁর বাবার বন্ধু রাজা রামমোহন রায়কে ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপূজায় আমন্ত্রণ জানাতে হাজির হয়েছিলেন নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে। বালক দেবেন্দ্র রামমোহনকে বলেন, ‘সামনে পূজা তাই তিনদিনই প্রতিমা দর্শনে আপনার নিমন্ত্রণ, পত্রে দাদুর এই অনুরোধ’।
ব্রাহ্ম রামমোহন রায় প্রতিমা পূজায় যার একেবারেই বিশ্বাস বা আস্থা নেই তিনি এই আমন্ত্রণে খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। যদিও বন্ধু দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে তিনি খুব স্নেহ করতেন তাই নিমন্ত্রণপত্রটি প্রত্যাখ্যান করেননি আবার সরাসরি সেটা গ্রহণও করেননি, তিনি তাঁর ছেলে রাধাপ্রসাদের কাছে দেবেন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রাধাপ্রসাদ পিতার হয়ে সেটা গ্রহণ করে দেবেন্দ্রনাথকে মিষ্টিমুখ করিয়ে দিয়েছিলেন।
এই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরমা অলকাসুন্দরী দেবীর কাছে মানুষ। ঠাকুরমার শালগ্রাম শিলার জন্য তিনি মালা গেঁথে দিতেন। স্নান করে তার সঙ্গে ছাদে দাঁড়িয়ে সূর্যমন্ত্র জপ করতেন। কালীঘাটে পূজা দিতে যেতেন। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘প্রথম বয়সে উপনয়নের পর প্রতিনিয়ত যখন গৃহেতে শালগ্রাম শিলার অর্চনা দেখিতাম, প্রতি বৎসরে যখন দুর্গাপূজার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম, প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর প্রার্থনা করিতাম, তখন মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরই শালগ্রামশিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী।’
দেবেন্দ্রনাথ যুবক হলে রাজা রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে এলেন। পৌত্তলিকতা ও প্রতিমা পূজার ঘোর বিরোধী হয়ে উঠলেন। তিনি সংকল্প করেছিলেন, ‘কোনো প্রতিমাকে পূজা করিব না, কোনো প্রতিমাকে প্রণাম করিব না, কোনো পৌত্তলিক পূজার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না। দেবেন্দ্রেনাথ তার ভাইদের সঙ্গে নিয়ে একটি পৌত্তলিকতা বিরোধী দলও গড়লেন।’ তাঁদের প্রতিজ্ঞা ছিল, ‘পূজার সময়ে আমরা দালানে কেহই যাইব না, যদি কেহ যাই, তবে প্রতিমাকে প্রণাম করিব না’।
১৮৩৯ সালে অক্টোবর মাসে দেবেন্দ্রনাথের বয়স যখন বাইশ বছর তখন তাঁদের বাড়িতে দুর্গাপূজা হচ্ছিল। সেবারেই তিনি পূজার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। তিনি পূজার সময়ে বাড়ির অন্যপ্রান্তে পুকুরের ধারে চুপ করে বসেছিলেন। সেখানে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে একেশ্বরবাদী তত্ত্ববোধিনী সভা গড়ে তুললেন। এরপর তিনি দুর্গাপূজার সময়ে কলকাতা ছেড়ে দেশ পর্যটনে বের হয়ে যেতেন। তিনি তাঁদের বাড়ি থেকে পূর্বপুরুষের চিরকালীন পূজা ও উৎসব উঠিয়ে দিতে পারেননি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোন সৌদামিনী দেবীর একটি লেখা থেকে জানা যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পূজার বাড়িতে থাকতেন না। পূজার সময় ঠাকুরবাড়িতে যত আচার-অনুষ্ঠানই হোক না কেন সেখানে রবিঠাকুরের মা স্বামীকে ছাড়া কোনোভাবেই নিজেকে শামিল করতে পারতেন না। ষষ্ঠীর দিন শুধু ছেলেমেয়েরাই নয়, আত্মীয়স্বজন, কর্মচারী, ভৃত্য এবং ঝিদের নতুন জামাকাপড় বিলি করে দেয়া হতো ঠাকুরবাড়ি থেকে।
রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেকালের ঠাকুরবাড়ির দুর্গোৎসব প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, পূজার দিনগুলোতে তাঁরা সন্ধ্যার দিকে দালানে যেতেন। সেখানে ধূপ জ্বালানো হতো। বিভিন্ন রকমের বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন বাদ্যযন্ত্রীরা। সন্ধ্যার আরতি দেখার জন্য এবং ঠাকুরকে প্রণাম করার জন্যই তাঁরা দালানে যেতেন। বিজয়ার দিন প্রতিমার নিরঞ্জনের মিছিলে ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা যোগ দিতেন।
মহর্ষি কন্যা সৌদামিনী দেবীর কথায়, ঠাকুরবাড়িতে যখন দুর্গোৎসব হতো তখন ছেলেরা বিজয়ার দিনে নতুন জামাকাপড় পরে প্রতিমার সঙ্গে যেত। আর মেয়েরা তখন তেতলার ছাদে উঠে প্রতিমা বিসর্জন দেখত। সৌদামিনী দেবীর লেখায় এও জানা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিজয়ার রাতে শান্তিজল সিঞ্চন ও ছোট-বড় সবার মধ্যে কোলাকুলি করাটা খুব পছন্দ করতেন। অবনীন্দ্রনাথের লেখা থেকে জানা যায়, বিজয়া তাঁদের জন্য খুব আনন্দের দিন ছিল। সেদিনও কিছু পার্বণী পাওয়া যেত।
ঠাকুরবাড়ির যত কর্মচারী ছিলেন সবার সঙ্গে তাঁরা কোলাকুলি করতেন। বুড়ো চাকররাও এসে ঠাকুরবাড়ির ছোট-বড় সবাইকে প্রণাম করত। পরবর্তীকালে ঠাকুরবাড়িতে অনুষ্ঠিত ‘বিজয়া সম্মিলনী’ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের লেখায় জানা যায়, সেদিন ঠাকুরবাড়িতে মস্ত জলসা বসত। খাওয়া-দাওয়া হতো খুব। ওস্তাদ তানপুরা নিয়ে গানে গানে মাত করে দিতেন ঝাড়বাতির আলোয় আলোকিত সেই ঠাকুরবাড়ি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতা দেবেন্দ্র ঠাকুরের প্রবর্তিত ব্রাহ্ম ধর্মাদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। তার ধর্মাদর্শে মূর্তি বা প্রতিমা পূজার কোনো স্থান ছিল না। বাংলাদেশের হিন্দুদের বড় উৎসব দুর্গাপূজায় কখনো শামিল হননি। তিনি উপনিষদের মনের মানুষের সন্ধানই করেছেন চিরকাল। তবে বাঙালিদের জীবনে দুর্গোৎসবের সামাজিকতা এবং মানবিকতার দিকটিকে তিনি প্রশংসা করেছেন।
ছিন্নপত্রে তিনি লিখেছেন, (পূজা উপলক্ষে) বিদেশ থেকে যে লোকটি এইমাত্র গ্রামে ফিরে এল তার মনের ভাব, তার ঘরের লোকদের মিলনের আগ্রহ এবং শরৎকালের এই আকাশ, এই পৃথিবী, সকালবেলাকার এই ঝিরঝিরে বাতাস এবং গাছপালা তৃণগুলো নদীর তরঙ্গ সবার ভিতরকার একটি অবিশ্রাম সঘন কম্পন, সমস্ত মিশিয়ে বাতায়নবর্তী এই একক যুবকটিকে (রবীন্দ্রনাথ) সুখে-দুঃখে একরকম চরম অভিভূত করে ফিরছিল। তিনি লিখেছেন, ‘বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বৃথা সময় নষ্ট। কিন্তু সমস্ত দেশে লোকে যাতে মনে করে একটা ভাবের আন্দোলন একটা বৃহৎ উচ্ছ্বাস এনে দেয় সে জিনিসটি কখনোই নিষ্ফল এবং সামান্য নয়।’
শুধু জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেই নয়, দুর্গাপূজা হতো পাথুরিয়াঘাটার সঙ্গীতপ্রিয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরিবারে, ধুমধাম করে পূজা হতো কয়লাঘাটার রমানাথ ঠাকুরের বাড়িতেও, তেমনি দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিটে রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বাড়িতে পূজা হতো। তবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পূজা কবে বন্ধ হয়ে যায় তা নিয়ে বহু মত আছে। কেউ বলেছেন যে ১৮৫৭, কেউ বলেছেন ১৮৫৮, আবার কেউ বলেছেন ১৮৭৫। সত্যি হলো এই যে, ১৮৫৮ থেকে পূজা চলে যায় শরিকদের নিয়ন্ত্রণে। ক্রমে বন্ধ হয়ে যায় ঠাকুরবাড়ির ঠাকুর পূজা।