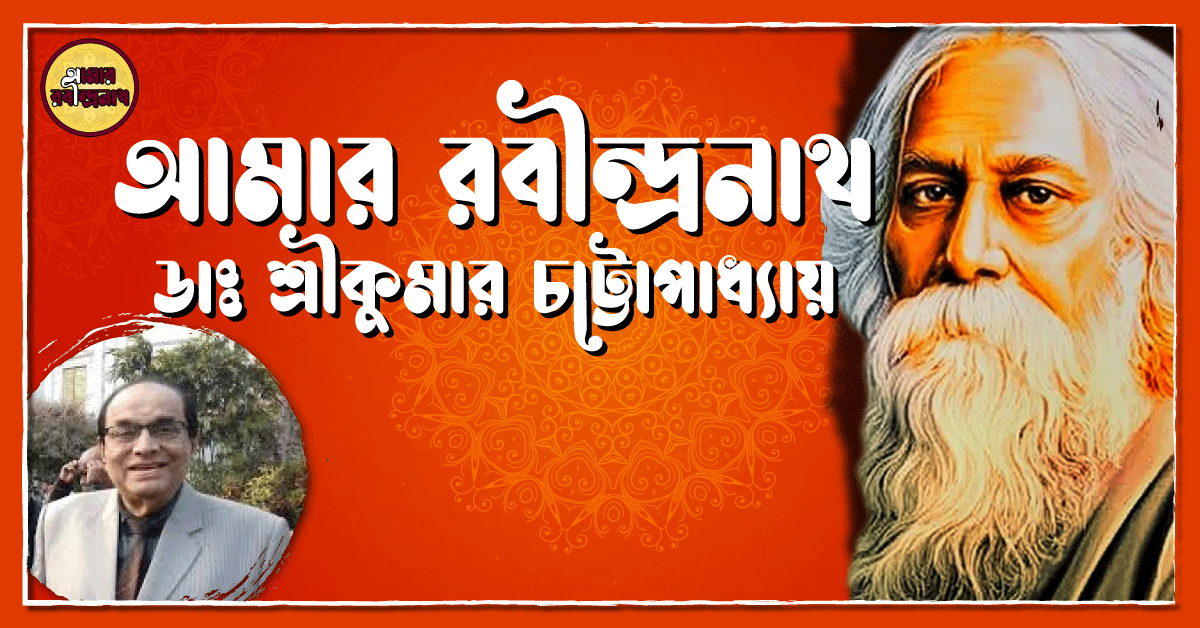প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, গবেষক ও প্রাবন্ধিক ডাঃ শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজচিন্তায় তাঁর গভীর বিশ্লেষণী দৃষ্টি এবং প্রাঞ্জল লেখনশৈলীর জন্য সমাদৃত। বহু বছর ধরে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্ত থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে আলোকিত করেছেন, পাশাপাশি প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র ও বক্তৃতার মাধ্যমে সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় সমৃদ্ধ অবদান রেখেছেন।
“আমার রবীন্দ্রনাথ” শিরোনামের নিবন্ধে ডাঃ শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পাঠ-স্মৃতির আলোকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। এখানে তিনি তুলে ধরেছেন কীভাবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, দর্শন ও মানবিকতা তাঁর চিন্তাধারা ও জীবনবোধকে গড়ে তুলেছে। একজন শিক্ষাবিদ ও গবেষকের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের তাৎপর্য এই লেখায় যেমন বিশ্লেষিত হয়েছে, তেমনি ধরা পড়েছে এক গভীর শ্রদ্ধা ও আত্মিক টান, যা পাঠককে ভাবনার নতুন দিগন্তে পৌঁছে দেবে।

রবীন্দ্রনাথের গান বিশ্ব সঙ্গীতের এক চিরন্তন সম্পদ। গানের প্রত্যেকটি কথার গভীরতার সঙ্গে সুরের সৌন্দর্যের অপূর্ব মেলবন্ধনেই রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদেরকে বারেবারে টানে। রবীন্দ্রনাথ এমন কিছু গানও তৈরি করেছেন যা, একেবারেই সাধারণ সুরের ওপর। সরাসরি সা রে গা মা পা ধা নি সা-র ওপর। যেমন ‘আলো আমার আলো ওগো/আলোয় ভুবন ভরা…’। অথচ অপূর্ব সৃষ্টি। কখনও কখনও মনে হয় এখনও একশো বছর এগিয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের গান। তাঁর গান আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গী। বিষণ্ণতার মাঝে অনুপ্রেরণা রয়েছে তাঁর গানে পাশাপাশি আনন্দের প্রকাশেও রবীন্দ্রনাথের গান।
রবীন্দ্র-নাথের কথার ওপর অন্য সুর বসাতে গেলে গানের শ্রুতিমধুরতা নষ্ট হবে, এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এই বিষয়ে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বছর কুড়ি আগে রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমির একটা ঘরে কয়েকজন শিল্পী বসে আছি। আমাদের আড্ডায় যোগ দিলেন সলিল চৌধুরী। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, ‘আমিও অনেক সিম্ফনি, অর্কেস্ট্রেশন করেছি, বিভিন্ন ধরনের সুরও করেছি। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের কাছে আমি হেরে গেছি।’ সবাই বলল, সে কী, কেন ? উত্তরে তিনি বললেন, “কয়েকদিন ধরে গীতবিতানে এমন একটা গান খুঁজছিলাম যে গানটা হবে অ্যাটিপিক্যাল।
টিপিক্যাল ধরনের ‘আমি তোমায় ভালোবাসি, চাঁদ- ফুল’ ইত্যাদির বাইরের গান।’ সলিলদা গানটার একটা কলি বললেন, ‘তুমি বাইরে থেকে দিলে বিষম তাড়া।/তাই ভয়ে ঘোরায় দিক্বিদিক,/ শেষে অন্তরে পাই সাড়া’। এই ‘তাড়া’ শব্দটি আমরা সচরাচর আধুনিক গানে ব্যবহার করি না। গানটাও খুব একটা পরিচিত না হওয়ায় সুর জানি না। ইচ্ছা করেই স্বরলিপি না খুলে রবীন্দ্র-নাথের কথার ওপর সুর দিলাম। সুর দিয়ে বেশ কয়েকজনকে শোনালাম।
সবাই বলল দারুণ হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথ কী সুর করেছেন তা জানার জন্য শেষে স্বরলিপি খুললাম। স্বরলিপি খুলতেই অবাক। দেখি রবীন্দ্র-নাথ যে আঙ্গিকে সুর দিয়েছেন, আমি তা কোনও সময়েই ভাবিনি। উনি গোটা গানটা বাউল অঙ্গে সুর দিয়েছেন। যেমন কথা তেমনই তার সুর। না, হবে না। রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে আর পারা যাবে না। হার স্বীকার করে নিলাম তাঁর কাছে।’
আজকাল ফিউশান গান নিয়ে মাতামাতি চলছে, অথচ রবীন্দ্র-নাথ প্রায় একশো বছর আগে ফিউশান সৃষ্টি করে গেছেন। কোনও কোনও গান ইমনে শুরু করে মাঝে পূরবীতে চলে গেছেন। ‘ডেকো না আমারে, ডেকো না।/চলে যে এসেছে কমনে তারে রেখো না।…’ ইমনে গানটা শুরু হয়ে যখন ‘আমার দুঃখজোয়ারের জলস্রোতে/নিয়ে যাবে মোরে সব লাঞ্ছনা হতে…’ পৌঁছাল তখন তিনি সুরটাকে পূরবীতে নিয়ে গেলেন। শেষে অন্তরায় গানটিকে আবার ইমনে নিয়ে গেলেন।
কখনওই মনে হয়নি সুরের বিকৃতি ঘটেছে। বেহাগ রাগের সঙ্গে কোমল নিষাদ লাগে না, কিন্তু এমন জায়গায় ওই কোমল নিষাদ লাগিয়েছেন, মনে হয়েছে ওটাই প্রাসঙ্গিক। দুই রাগকে এমনভাবে মিশিয়েছেন যা সাধারণভাবে অসম্ভব। আজ থেকে কতদিন আগে তিনি এই অনবদ্য সৃষ্টি করে গেছেন। ধরা যাক ‘সঘন গহন রাত্রি, ঝরিছে শ্রাবণ ধারা’ গানটির কথা। গানটা মল্লার রাগে যেতে যেতে যখন অন্তরা দিয়ে গানটাকে নামাচ্ছেন তখন কোমল ধৈবৎ দিয়ে হঠাৎই মধ্যমে শেষ করলেন।
মধ্যমই যেন বাদীস্বর হয়ে গেল। আবার ‘এবারের মুখর হলো কেকা ওই’ গানটিকে শুরু থেকে অন্তরা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন কাফি দিয়ে। কিন্তু সঞ্চারীতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোমল রেখাবে শেষ করলেন। সাধারণভাবে কাফির সঙ্গে কোমল রেখাব মেশে না। কিন্তু তিনি বিকৃত না করেই আশ্চর্যজনকভাবে দুটি রাগের ফিউশন ঘটালেন। মনে হয়নি সুরটার কোনও পরিবর্তন হয়েছে। আবার বিদেশি গানের সুর যখন ব্যবহার করেছেন, তখন পরদার ওঠানামার ওপরেও বৈচিত্র্য এনেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ধারার গানের সুরকে ব্যবহার করেছেন তবে তা স্বকীয় আঙ্গিকেই।
একটি অভিজ্ঞতার কথা জানাই। বহুদিন আগে দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। বিখ্যাত কত্থক শিল্পী পণ্ডিত দুর্গালাল আমার গান শুনে ‘তোমার কটি-তটের ধটি-কে দিল রাঙিয়া’ গানের চলন সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। এই গানটা ঝম্পক তালের হলেও উনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘দাদা ইয়ে ক্যায়সা তাল হ্যায় ? ইয়েতো ঝাঁপতাল উলাট যাতি হ্যায়।’ কিন্তু গানটি ঝম্পক তালের হলেও এর ছন্দ ১২৩, ১২। ধিধিনা, ধিনা। আর ঝাঁপতাল হল ১২, ১২৩।
ঠিক উলটো, ধিনা, দ্বিধিনা। পণ্ডিত দুর্গালাল তো এই তালের ছন্দ শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি? তখনই তিনি আমার তবলাবাদককে এই ঝম্পকতালের তাল বাজাতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর বোল বলতে লাগলেন। এই তালে কখক নাচ তুলে অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করলেন। সে কে অপূর্ব অনুষ্ঠান। বাইরে যখনই অনুষ্ঠান করতে গিয়েছি, দেখেছি শ্রোতারা তো বটেই উচ্চাঙ্গ শিল্পীরাও রবীন্দ্রনাথের সুরের বৈচিত্র্য, তালের ছন্দে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।
রবীন্দ্রনাথের গান কেন এখনও সমকালীন? এই প্রসঙ্গে বলতে পারি, পাঁচ বা চার দশক আগের বাংলা বা আধুনিক গানের ধরন একরকম। আজ অন্যরকম। গান শুনলেই বোঝা যায় কোন সময়ের গান। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোনও পরিবর্তন আছে কি? রবীন্দ্রনাথের কোনও গান শুনলে মনে হয় এটা পুরোনো দিনের সুর? অথচ এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে পরম্পরার পর পরম্পরা কণ্ঠে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই অনির্বচনীয় সঙ্গীত ধারাকে। আসলে সময়কে উত্তীর্ণ করে তিনি সৃষ্টি করেছেন।
ইদানীং কোনও কোনও শিল্পী স্বরলিপি অনুযায়ী না গান গেয়ে, গানের মধ্যে অহেতুক রাগ টেনে আনছেন। আসলে রবীন্দ্র-নাথের ওপর নিজের দক্ষতা প্রকাশ করতে চাইছেন। এতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে ভালো লাগছে কি? এটা আমার প্রশ্ন। একবার কথা প্রসঙ্গে এই সময়ের এক শিল্পীকে আমি বলেছিলাম, স্বরলিপির বাইরে গিয়ে গানের মধ্যে অতিরিক্ত কাজ লাগানোর কোনও প্রয়োজন আছে কি? অথচ স্বরলিপি অনুযায়ী যেখানে কাজের প্রয়োজন সেখানে এড়িয়ে চলেছ। এর কোনও উত্তর তিনি দেননি। তাই রবীন্দ্র-নাথের গানকে বিকৃত করে গাওয়া কারোর পক্ষেই উচিত হবে না বলে আমি মনে করি।
উনি যা সৃষ্টি করে দিয়েছেন তা স্বয়ংসম্পূর্ণ। ক্ল্যাসিক ক্যান নট বি চেঞ্জড, ধ্রুপদীর পরিবর্তন হয় না। চার্লি চ্যাপলিনের পোশাক পরিবর্তন করে বা মোনালিসার হাসিকে মুছে দিয়ে নতুনভাবে কেউ উপস্থিত করতেই পারেন। কিন্তু মানুষ তা বর্জনই করবেন। তবে, সময়ের সঙ্গে বদলাচ্ছে সমাজ। বাড়ছে জীবনের গতিও। তার মধ্যেও স্থান করে নিয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান। এর মধ্যে গায়কীর কি পরিবর্তন হয়নি? হয়েছে। কে এল সায়গল, কানন দেবী কিংবা পঙ্কজকুমার মল্লিক যে ঢঙে রবীন্দ্রসঙ্গীতে গাইতেন এখনকার শিল্পীরা কি একই ঢঙে গাইবেন? গায়কীরও পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তারও একটা সীমারেখা রয়েছে। ওই সীমারেখার মধ্যেই গায়কীর পরিবর্তন করেই রবীন্দ্রসঙ্গীতকে পরিবেশন করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের গান একটা মর্যাদার প্রতীক হয়ে গেছে।
আমি রবীন্দ্রনাথের গান গাই বলে সমাজ থেকে সমীহ আদায়ের চেষ্টা করলে সেটা বোকামিই হবে। রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গেলে রেওয়াজের প্রয়োজন। অথচ এখনকার অনেক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই দেখি রেওয়াজের ঘাটতি। দেখা যাচ্ছে গলা তৈরি না করেন কঠিন কঠিন গান গাইছে। গানগুলো খুবই বেমানান লাগছে। এখন টাকা দিয়ে সিডি, ক্যাসেট হয়ে যাচ্ছে, এতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে বলেই মনে করি। তার মধ্যেও সিরিয়াস ছাত্রছাত্রী রয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গেলে তার আঙ্গিককে মর্যাদা দিয়েই গান গাইতে হবে। ধৈর্যের সঙ্গে শেখার মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্র-নাথের গান গাওয়ার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।
পাশাপাশি উৎসাহও রয়েছে শেখার ক্ষেত্রে। শ্রোতাদের মধ্যেও। তাঁর গান জড়িয়ে আছে আমাদের জীবনের সুখেদুঃখে। থাকবেও বছরের পর বছর ধরে। যুগ থেকে যুগান্তরে।