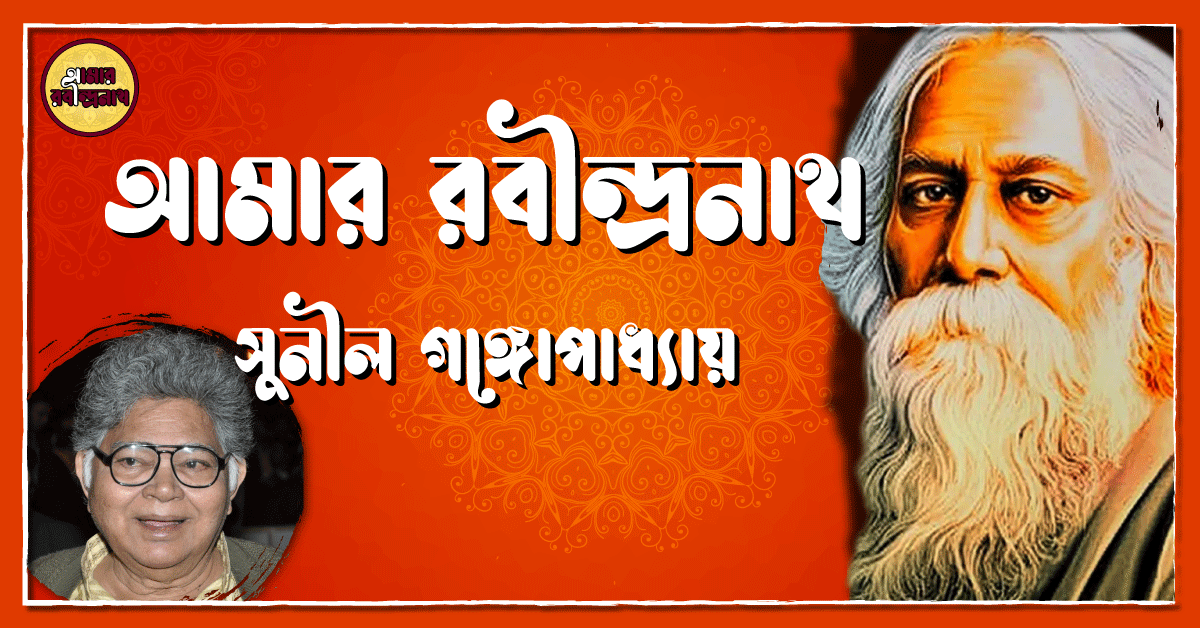আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যসম্পাদক হিসেবে সমান খ্যাত। তাঁর সৃষ্টিশীল ভুবনে মিশে আছে প্রেম, মানবজীবনের অনন্ত অনুসন্ধান, ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ও গভীর জীবনদর্শন। সেই সময়, প্রথম আলো, সেই চোখ, নীললোহিত সিরিজসহ অসংখ্য উপন্যাস ও কাব্যগ্রন্থ তাঁকে বাংলা পাঠকের কাছে এক অনন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।
“আমার রবীন্দ্রনাথ” শিরোনামের নিবন্ধে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ব্যক্তিগত স্মৃতি, সাহিত্যিক অনুরাগ ও পাঠ-অভিজ্ঞতার মিশেলে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁর চোখে দেখা রূপে। এখানে তিনি প্রকাশ করেছেন, কীভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান ও প্রবন্ধ তাঁর সাহিত্যজীবন ও মননকে প্রভাবিত করেছে, এবং কীভাবে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা তাঁর নিজের সৃজনশীলতার সঙ্গে সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। এই লেখা পাঠকের কাছে হবে এক সাহিত্যিক মননের অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথ অন্বেষণ।

১৮৭৩ সালের ভাদ্র মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ‘আয়-ব্যয়’-এর একটি হিসেব ১ দেওয়া হয়েছিল। তাতে দেখা যাচ্ছে যে, এই পত্রিকার শুভার্থী দাতাদের ছাপা নামের তালিকায় জনৈক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। ইনি দান করেছেন দু’টাকা বারো আনা তিন পয়সা। এই বিশাল দাতাটি কোনও পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি নন, সাড়ে বারো বছর বয়েসের একটি বালক মাত্র।
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে ডালহাউসি পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন, কিছুদিন পর তিনি ছেলেকে ফেরত পাঠিয়ে নিজে রয়ে গেলেন সেখানে। রাহা খরচ বাবদ ছেলের হাতে কিছু টাকা দিয়েছিলেন, তার থেকে যা বেঁচেছিল তা লক্ষ্মীছেলের মতন সেই ছেলে জমা দিয়ে দেয় কলকাতার বাড়ির খাজাঞ্চিখানায়। কিছুদিন পরে কর্তাবাবুর নির্দেশে সেই টাকা থেকে ছ’টাকা ফেরত দেওয়া হয় বালক রবীন্দ্রকে, বাকি টাকা তার নামে দান হিসেবে জমা পড়ে তত্ত্ববোধিনী ফান্ডে।
ঘটনাটি স্মরণযোগ্য এই কারণে যে, সেই প্রথম ছাপার অক্ষরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম দেখা যায়। রবি নামের ওই বালকটির নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখার ঝোঁক ছিল আরও আগে থেকেই। ব্রাহ্মসমাজের ছাপাখানায় টাইপ খুঁজে খুঁজে নিজের নাম সাজিয়ে তাতে কালি মাখিয়ে কাগজের ওপর ছাপ দিয়ে দেখতে তার ভালো লাগত, এই ঘটনার উল্লেখ আছে জীবনস্মৃতিতে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা যখন ছাপা হয় তখন তার নীচে অবশ্য কবির নাম ছিল না।
সে সময়ে নামহীন রচনা প্রকাশের রীতি ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত রচনা ঠিক কোনটি তা নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে আজও কিঞ্চিৎ বিবাদ থাকলেও মোটামুটি এখন নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বঙ্গদর্শন পত্রিকায় দ্বিতীয় বর্ষের দশম সংখ্যায় প্রকাশিত ‘ভারত-বিলাপ’ নামে অনামা কবির রচনাটিই ভবিষ্যতের এক মহাকবির সৃষ্টি। কবিতাটির তলায় সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র নোট দিয়েছেন, “এই কবিতাটি এক চতুর্দশ বর্ষীয় বালকের রচিত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কোনও কোনও স্থানে অল্পমাত্র সংশোধন করিয়াছি। এবং কোনও কোনও অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি।”
এই কিশোর কবির বয়েস অবশ্য তখনও চোদ্দো হয়নি, বারো-সাড়ে বারোর বেশি না, বয়েসের তুলনায় তাঁকে বড় দেখাত। বঙ্কিম সম্ভবত এই কিশোর কবিকে চোখেও দেখেছিলেন, কেননা এঁর বড় দাদা ছিলেন বঙ্কিমের বন্ধু এবং সেই সূত্রে ঠাকুরবাড়িতে বঙ্কিমের যাতায়াত ছিল। এমন কল্পনা করা যেতে পারে যে, ঠাকুরবাড়িতেই দ্বিজেন্দ্রনাথ কোনও একদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন, দেখুন দেখুন বঙ্কিমবাবু, আমার কনিষ্ঠ ভাই রবি কেমন মনোমুগ্ধকর কবিতা রচেছে।
বাংলা ভাষার শেষ্ঠ সম্পাদক কিছু সংশোধন করে ছাপলেন এক বালকের কবিতা, যে একদিন জগৎ-বিখ্যাত হবে। কিন্তু সেই প্রথম কবিতাটিই যে আলোড়ন তুলেছিল, তার তুলনা পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্যে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। সেই বালকের কবিতা নিয়ে তৎকালীন দুটি বিখ্যাত পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখা হয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ কবিতাটির সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। সোমপ্রকাশ পত্রিকায় শিবনাথ শাস্ত্রী আবার আকারে ইঙ্গিতে ওই কবিকে এঁচোড়ে পাকা বলে ছেড়েছেন। দুরকম প্রতিক্রিয়া হলেও এক বালকের প্রতি দুজন বাঘা সম্পাদকের এতখানি মনোযোগ! নাম না ছাপা হলেও ওই কবিতার কবিকে যে দুজনেই চিনতে পেরেছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।
প্রায় বালক বয়েস থেকেই রবীন্দ্রনাথ এসে পড়েছিলেন যাকে বলে পাদপ্রদীপের আলোয়। পারিবারিক পটভূমিকাই তার প্রধান কারণ বটে, কিন্তু সে অতিরিক্ত সুযোগ তো তাঁর অন্য ভ্রাতাদেরও ছিল। যদিও কিশোর রবির রচনাগুলি সাংঘাতিক চমকপ্রদ কিছু নয়, কিন্তু খানিকটা নতুন প্রতিভার ছাপ তাতে রয়েছে। যে-বছর রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতাটি ছাপা হয়, সেই বছরই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে নিঃস্ব, রিক্ত অবস্থায় মৃত্যু হয় মাইকেল মধুসূদনের।
বাংলার সবচেয়ে সাড়া জাগানো কবি শোচনীয় ভাবে ঝরে গেলেন অকালে, সেই বছরই যে নবীন রবির উদয় হল তিনি যে শুধু সমগ্র সাহিত্যাকাশ দখল করবেন তাই-ই নয়, মাইকেলের প্রভাবও যে একেবারে মুছে দেবেন, তা কি বোঝা গিয়েছিল? মাইকেল চলে গেলেও তখন হেম-নবীনের খুব রবরবা। নবীনচন্দ্র সেন তাঁর আত্মজীবনীতে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখার বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে কলকাতার উপকণ্ঠে ‘ন্যাশনাল মেলা’ দেখতে গিয়েছিলেন।
সেখানে মেলার এক কোণে একটি প্রকাণ্ড গাছের নীচে ‘সাদা ঢিলা ইজার-চাপকান পরা’ এক সুন্দর নব যুবককে দেখতে পেলেন, বয়েস আঠারো-উনিশ। প্রথম দর্শনেই নবীনচন্দ্রের মনে হল “বৃক্ষতলায় যেন এক স্বর্ণ-মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে।” পরে সে নব যুবকের কবিতা পাঠ ও গান শুনে তিনি একেবারে মোহিত। দু-একদিন পরে চুঁচড়োয় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে নবীনচন্দ্র সেই প্রসঙ্গ তুলতেই অক্ষয়চন্দ্র বললেন, “কে? রবি ঠাকুর বুঝি? ও ঠাকুরবাড়ির কাঁচা মিঠা আঁম!” নবীনচন্দ্ৰ যদিও রবীন্দ্রনাথের বয়েস আঠারো-উনিশ ভেবেছিলেন, কিন্তু হিসেব অনুযায়ী তখন তাঁর বয়েস পনেরোর বেশি না! নবীনচন্দ্র চাকরির কারণে বাইরে বাইরে ঘুরতেন, তাই রবীন্দ্রনাথকে চাক্ষুষ চিনতেন না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই পনেরো বছর বয়েসেই রবীন্দ্রনাথ রীতিমতন বিখ্যাত।
পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হওয়ার পর নবীনচন্দ্ৰ আফশোস করেছিলেন এই ভেবে যে, রবীন্দ্রবাবু শুধু লিরিক লিখে প্রতিভার অপচয় করছেন, তিনি মহাকাব্য লেখেন না। তাতে বাংলা ভাষার ক্ষতি হচ্ছে। নবীনচন্দ্র কিছুই বুঝতে পারেননি যে ওই লিরিক লেখকটিই একদিন তাঁর মতন সবক’টি মহাকাব্য রচয়িতাকে ম্লান করে দেবেন।
শুধু কবিতার জন্যই অল্প বয়েস থেকেই এতটা খ্যাতি নয় নিশ্চিত, ঠাকুরবাড়ির এই রূপবান সন্তানটির আচরণ অতি বিনীত, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, তদুপরি তিনি নিজে গান রচনা করেন। তাঁর ‘মধুর কামিনীলাঞ্ছন কণ্ঠে’ গান শুনে সকলেই মুগ্ধ। তৎকালীন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগৎটি বেশ ছোট, মুখে মুখে এই নবযুবকটির গুণপনা সম্পর্কে বার্তা রটে যায়।
কবিতা ও গানের পরেই আসে নাটক। সদ্য যৌবন থেকেই তিনি শুধু নাটক রচনায় মন দেননি, নিজে অভিনয়ও করেছেন, বিভিন্ন ভূমিকায় দক্ষ অভিনেতা। প্রথম যৌবনে তিনি গায়ক ও নট-নাট্যকার হিসেবেই বেশি প্রতিষ্ঠা পান। এই সময়কার কবিতাগুলি অতি রোমান্টিক, যেন মনে হয় এই কবিতাগুলি শুধুই নিভৃতে পড়বার মতন নয়। যিনি লিখেছেন তিনিও নিভৃতচারী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তখন আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছেন বাইরে, পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে, ব্রাহ্ম সমাজ ছাড়িয়ে চলে আসছেন বৃহত্তর সমাজে।
ঠাকুরবাড়ির অন্য ছেলেরাও সুযোগ-সুবিধে পেয়েছেন অনেক, টাকা পয়সা বোধহয় রবীন্দ্রনাথের থেকে বেশিই পেয়েছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নানা হুজুগে অপব্যয় দেখে তাই-ই মনে হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতন অন্য আর কারুরই দেশ সম্পর্কে সামগ্রিক চিন্তা ছিল না। শুধু কবি বা সাহিত্যস্রষ্টাই নয়, চিন্তানায়ক হিসেবেও তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটতে লাগল ধীরে ধীরে। যেন তিনি জানতেন যে তিনি বহুদিন বাঁচবেন, তাই রবীন্দ্রনাথের কোনও তাড়াহুড়ো ছিল না।
ঠাকুরবাড়ির ছেলে হিসেবে যতটা খ্যাতি পাওয়ার কথা, তা তিনি পেয়ে গেছেন প্রথম দিকেই, তারপর তাঁকে সব কিছুই অর্জন করতে হয়েছে। প্রথমে তিনি বাংলার মন জয় করেছেন, তারপর তাঁর কীর্তি ও ব্যক্তিত্বের পরিব্যাপ্তি হয়েছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, তারপর তিনি পা বাড়িয়েছেন বিশ্বের দিকে। গ্রীষ্মের দুপুরে খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে তিনি যখন নিজের কবিতার ইংরেজি তর্জমা করেছিলেন, সেই সময় তাঁর বড়দাদা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিলেন, তুই নিজে থেকে এসব করতে যাচ্ছিস কেন, সাহেবদের যদি প্রয়োজন হবে, ওরা নিজেরা অনুবাদ করে নেবে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠিক বুঝতে পারেননি, সাহেবদের কোনও প্রয়োজন ছিল না, তারা নিজেরা তাদের পদানত দেশে কোনও কবিকে সম্মান জানাবার জন্য ব্যগ্র ছিল না।
একটি পরাধীন দেশের নাগরিককে বিশ্ববাসীর কাছে প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে শুধু প্রতিভা নয়, অসীম ধৈর্য ও পরিশ্রমেরও প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথ যে বইয়ের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন, আমরা বাঙালিরা জানি, সেটি তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নয়। গোটা বাংলা সাহিত্যে গীতাঞ্জলির স্থান নগণ্য। বাংলা গীতাঞ্জলি ও ইংরেজি গীতাঞ্জলি অবশ্য এক নয়, নামটি অপরিবর্তিত রেখে রবীন্দ্রনাথ ইংরিজি গীতাঞ্জলিতে তাঁর অন্য কিছু কবিতাও জুড়ে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও ইংরেজি গীতাঞ্জলিকে খুব একটা উচ্চ মূল্য দেওয়া যায় না।
সাহেবরা কীজন্য ওই বই পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন তা বলা শক্ত। কেউ কেউ বলেন, যুদ্ধের আগেকার ইউরোপের অশান্ত পরিবেশে ওইসব অধ্যাত্মরসের কবিতাগুালি পড়ে ওরা শান্তি পেয়েছিল। হতেও পারে। তবে, ইয়েটস-এজরা পাউন্ডের যে অধ্যাত্মরসের দিকে তখন খুব ঝোঁক ছিল এমন বিশ্বাস করা শক্ত। আঁদ্রে জিদ রবীন্দ্রনাথের নাটক পড়ে মুগ্ধ হয়ে নিজে অনুবাদ করেছিলেন ‘ডাকঘর’।
যে-বইয়ের জন্যই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হোক, এতে কোনওই সন্দেহ নেই সারা পৃথিবীতে তখন রবীন্দ্রনাথের মতন এত বিশাল মাপের লেখক আর একজনও ছিলেন না। সে বছর তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী টমাস হার্ডির চেয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্তত দশ গুণ বড়। সেই বাহান্ন বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ প্রায় একক প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের মান এনেছেন প্রথম সারিতে। তিনি কবিতা ভালো লিখেছেন না ছোটগল্প ভালো লিখেছেন, এরকম প্রশ্নও অবান্তর, কারণ কবিতায়-গল্পে-উপন্যাসে-প্রবন্ধে- নাটকে-গানে-লঘু রচনায় বাংলার সংস্কৃতিকে মাতিয়ে রেখেছেন।
প্রচুর লিখেছেন তিনি, তার কোনওটাই একেবারে অপাঙ্ক্তেয় তো নয়ই, এমনকী দ্বিতীয় শ্রেণিরও বলা যাবে না, ভাষা ব্যবহার ও সুরুচিতে সবই প্রায় প্রথম শ্রেণির। একজন লেখক সাহিত্যের কোনও একটি শাখাও বাদ দেননি এবং কোনওটিতেই বিফল হননি, এইরকম দ্বিতীয় লেখক আর পৃথিবীতে পাওয়া যাবে কি? নোবেল প্রাইজের প্রসঙ্গে একটি কথাই বিশেষভাবে বলা যায়। বাংলা ভাষার পাঠক তথা ভারতীয় পাঠকরা রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে জানে, তাঁর বিশালত্ব যেভাবে অনুধাবন করতে পারে, বিদেশিরা সে তুলনায় রবীন্দ্রনাথকে কতটুকু জেনেছে? যদি পুরোপুরি রবীন্দ্রনাথকে তারা জানতে পারত, তা হলে তো তারা রবীন্দ্রনাথকে মাথায় নিয়ে নাচত। রবীন্দ্রসংগীতের মর্মই তো ওরা বুঝল না।
ইস, ওদের কী দুর্ভাগ্য। দেশের লোকও অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে মাথায় নিয়ে নাচেনি। নোবেল পুরস্কারের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে গেলে বেরিয়ে পড়ল অনেক হিংস্র দাঁত ও ধারাল নখ। নির্লজ্জ পরশ্রীকাতরতায় এদেশের মানুষ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। মানসিক ভাবে যারা বামন তারা লম্বা লোকদের সহ্য করতে পারে না। নিজেরা বড় হওয়ার চেষ্টা না করে তারা চায় বড় মানুষের মাথা কেটে ছোট করতে। এরন্ড বনে এক মহাদ্রুম, সমস্ত ঝড়-ঝাপটা তিনি মাথা পেতে নিয়েছেন, কিন্তু তা হননি ।
রবীন্দ্রনাথের কিছু ভক্ত ও চাটুকার তাঁকে সবসময় ঘিরে থাকত, তারা তাদের গুরুদেবের দৃষ্টিকে কিছুটা আড়াল করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু উপকার করেনি। যখন তাদের সাহায্যের যথার্থ প্রয়োজন ছিল তখন তারা পিছু-পা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ পক্ষে কিন্তু পাওয়া যাবে অনেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এই শতাব্দীর বিখ্যাত বাঙালিদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ ও সুভাষচন্দ্র বসু ছাড়া রবীন্দ্রনাথের শত্রুতা বা নিন্দা করতে বাকি রেখেছেন কে? যাঁদের রবীন্দ্রনাথ বন্ধু মনে করতেন, যাঁদের তিনি কাছে টেনেছিলেন, তাঁরাও বিরূপ হয়েছেন এক সময়।
যেমন জগদীশ বসু, যেমন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তিনি শরৎচন্দ্র ও নজরুলকে সস্নেহে নিজের বই উপহার দিয়েছেন, নজরুল যখন জেলখানায় গিয়ে অনশন করেছিলেন তখন উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ তার পাঠিয়েছিলেন তাঁকে, এঁরাও রবীন্দ্রনাথের সামনে এসে যথেষ্ট ভক্তি প্রদর্শন করলেও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কলম ধরতে দ্বিধা করেননি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন অবলীলায়। সুরেশ সমাজপতি, সজনীকান্ত দাসদের কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়, পরনিন্দাই এদের পেশা, কিন্তু বিপিনচন্দ্র পাল, যদুনাথ সরকারের মতন মানুষও কটূক্তি করেছেন নানাভাবে। অনেকেই শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গেছেন, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে মিথ্যে কালিমা লাগাতেও দ্বিধা করেননি। যেমন ডি এল রায়। এ ছাড়া কত পত্র-পত্রিকা যে কাদা ছিটিয়েছে তার ঠিক নেই। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যেই দেখা গেল, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রভাব মুছে ফেলার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।
শুধু তাঁর মতন বনস্পতিই আড়ালে পড়ে গেলেন না, শরৎচন্দ্র- নজরুলের ধারাও রুদ্ধ, ওই জীবনানন্দ-মানিক-প্রেমেন্দ্রর দল যে আধুনিক সাহিত্যের পত্তন করেছেন তাই-ই দিনে দিনে কালকেতুর মতন বাড়ছে। রবীন্দ্রমানস ও আধুনিক সাহিত্যের সংঘর্ষ বেশ কিছুদিন চলেছিল। সমালোচকরা এই আধুনিক সাহিত্যকে আঁতুড়ে নুন খাইয়ে মারতেও উদ্যত হয়েছিল। পাঠকরা কিন্তু আধুনিক সাহিত্যকে বর্জন করেনি, বিতর্ক চলতে থাকলেও পাঠকশ্রেণি সামসাময়িক কালের প্রতিচ্ছবি ও চিন্তার প্রতিফলনকে অগ্রাহ্য করতে পারে না।
পণ্ডিতেরা এবং উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালি বাবু সমাজ আরও অনেকদিন অবশ্য রবীন্দ্র-সর্বস্বতা আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন, তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ আর শুধু লেখক নন, পূজনীয় গুরুদেব। কোনও কোনও অতি পণ্ডিত এমন কথাও বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে আর কিছুই পড়ার নেই, রবীন্দ্রনাথের পর আর বাংলা কবিতা লেখাই হয়নি। কোনও জীবিত চলমান ভাষা সম্পর্কে অন্য কোনও দেশে কোনও যথার্থ পণ্ডিত এমন কথা বলতে পারেন, বিশ্বাসই করা যায় না। কিন্তু এদেশে সুকুমার সেন, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ এরকম বলেছেন।
বিদেশে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা পড়ে যেতে থাকে হু-হু করে। প্রথম . মহাযুদ্ধের আগে যে সব রচনা নিয়ে হইচই হয়েছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেগুলি নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে চায় না। ইংরেজিতে অনূদিত হলেও রবীন্দ্র রচনাবলী মূল ইংরেজি সাহিত্যের অন্তর্গত হয়নি, ক্লাসিকস হিসেবে গণ্য হওয়া তো দূরের কথা। মার্কিন দেশের পাঠকরা রবীন্দ্রনাথকে ভালো করে ছুঁয়েও দেখেনি।
ষাটের দশকে লন্ডনে ফেবার অ্যান্ড ফেবার কোম্পানির অফিসে টি এস এলিয়টের সঙ্গে আমার স্বল্পকালীন সাক্ষাতের সময় রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ওঠায় তিনি স্মিত হেসে বলেছিলেন, নট মাই কাপ অফ টি। এলিয়টের মতো প্রবীণ কবিই যদি এমন রবীন্দ্র অনাসক্তি দেখান, তা হলে তৎকালীন তরুণ কবিদের মনোভাব সহজেই অনুমেয়। আমরা নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িয়ে বিদেশে গর্ব করতে যাই। কিন্তু পশ্চিমে ওই পুরস্কারের সম্মান অনেক কমে গেছে। বছরে একবার দিন কয়েকের জন্য ওই পুরস্কার নিয়ে আলোচনা শোনা যায়, তারপর কোন লেখক কবে ওই পুরস্কার পেয়েছে তা অনেকেই ভুলে যায়।
একমাত্র সোভিয়েত দেশেই রবীন্দ্রচর্চা এখনও অব্যাহত আছে কোনও অজ্ঞাত কারণে। সেখানকার পাঠকরা রবীন্দ্রনাথকে পছন্দ করে। রবীন্দ্র রচনাবলীর একটি পাঁচ লক্ষ কপির সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, সেদেশে কোনও দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছ থেকে একথা আমার নিজের কানে শোনা
১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর বছরে খুব ঢাকঢোল বাজিয়ে উৎসব করা হল, তারপর পাকাপাকিভাবে তাঁকে ছবি করে ঝুলিয়ে দেওয়া হল দেওয়ালে, তাঁর গ্রন্থাবলী চাবিবন্ধ করে রাখা হল আলমারিতে। যে কোনও বাড়ির আলমারিতে রবীন্দ্র রচনাবলী না থাকলে খুবই বেমানান লাগে। সেইজন্য সরকার থেকে সুলভ মূল্যে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের কথা ঘোষণা করা হলেই বিরাট লাইনে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। জীবৎকালে সবক’টি খণ্ড পাওয়া যাবে না জেনেও উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যেতে চায় বলে লোকে এই রচনাবলীর গ্রাহক হয়।
এই সময়কার সাহিত্য থেকে রবীন্দ্রনাথের ছাপ মুছে গেলেও বাংলার সংস্কৃতি জগতে তিনি একচ্ছত্র অধিপতি। যে কোনও সাংস্কৃতিক উৎসবে, এমনকী বিবাহ বা শ্রাদ্ধবাসরেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্থান অবধারিত। তাঁর নাটক কোথাও না কোথাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে সারা বছর। তাঁর কাহিনি-ঘেঁষা কবিতাগুলি আবৃত্তিকারদের কণ্ঠে জনপ্রিয়। একমাত্র রবীন্দ্র-নৃত্যটাই তেমন সুবিধের নয়। স্কুল-কলেজের বাইরে তেমন জমে না ।
রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি আধুনিক রুচিতে অনেকটাই ভাবালুতাপূর্ণ মনে হলেও তাঁর, পরে আর কেউ উল্লেখযোগ্য নাটক লেখেননি। রবীন্দ্রনাথ তবু নাটক নিয়ে নানান পরীক্ষা করেছেন, একালের পরীক্ষামূলক সব নাটকই আমদানি করতে হয় বিদেশ থেকে। আধুনিক কবিরা বাংলা গান রচনার দিকে গেলেনই না একেবারে। গীতিকার ও সুরকার আলাদা হয়ে যাওয়াই এর একমাত্র কারণ হয়তো নয়। আধুনিক গানে শচীন দেববর্মণ এবং সলিল চৌধুরী বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দি সিনেমার জগৎ তাঁদের টেনে নিয়ে গেল এবং চুষে ছিবড়ে করে ছাড়ল। তাঁদের কোনও উত্তরসূরিও পাওয়া গেল না।
ষাটের দশকের মাঝামাঝি বাংলার অন্য খণ্ডে, পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মহা শোরগোল পড়ে যায়। সেখানকার হঠকারী সরকার জোর করে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার বন্ধ করে দিতে গেল। বাধা দিলেই প্রতিবাদ প্রবল হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার প্রয়াসের ফলেই সেখানকার সংস্কৃতিপ্রেমীরা নবোদ্যমে রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরলেন। রবীন্দ্রচর্চার জোয়ার এসে গেল সেখানে। অনেকের গদ্য ভাষায় দেখা গেল রবীন্দ্র গদ্যরীতির প্রভাব, রবীন্দ্রসঙ্গীতে এল নতুন উদ্দীপনা। সেখানকার বিরোধীপক্ষই যখন জয়ী হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ল, তখন তার জাতীয় সঙ্গীত হল “আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।”

এদিকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীতও রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, তা হলেও এদেশের মানুষ যাতে সে গান ভুলে না যায়, তাই ভারত সরকার প্রতিটি সিনেমা হলে জাতীয় সঙ্গীত বাজাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সশ্রদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত শোনার বদলে দর্শকরা শো শেষ হতে না-হতেই পড়ি কি মরি বলে দৌড়ত। শেষ পর্যন্ত কিছুদিন পর সেই প্রহসন বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখানকার বেতারে টিভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার অবাধ, প্রতিদিন রাখাটাই যেন বাধ্যতামূলক। তাই দলে দলে গায়ক-গায়িকা নিছক যান্ত্রিক সুরে গান গেয়ে যায়। নতুন ভাবে পরিবেশনে কোনও চিন্তাই নেই। তরুণ সাহিত্যিক মহলে রবীন্দ্রনাথের নাম কদাচিৎ উচ্চারিত হয়। রবীন্দ্র বিরোধিতার কোনও প্রশ্নই নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন সমগ্র পটভূমিকা জুড়ে।
বাংলা ভাষা নিয়ে যিনি লেখালেখি করবেন, তিনি সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য মাথায় না রাখলে নতুন কিছু লিখবেন কী করে? সারা জীবনে গান লিখেছেন প্রায় আড়াই হাজার, কবিতা দেড় হাজার, ছোটগল্প একশোর কিছু কম, উপন্যাস তেরোটি, নাটক- গীতিনাট্য-নৃত্যানাট্য মিলিয়ে প্রায় ছত্রিশটি। এ ছাড়া প্রবন্ধের পাহাড়, ভ্রমণকাহিনির নদী ও চিঠিপত্রের পত্ররাজি সংখ্যাতীত। ছোটগল্প অল্প বয়েসেই লিখেছেন বেশি। যেমন ছবি আঁকতে শুরু করলেন বেশি বয়েসে। এই দুটি বিষয়ে তাঁর খুব যেন একটা আত্মবিশ্বাস ছিল না।
অথচ ছোটগল্পে তিনি আজও অপরাজেয় । তিনি গ্রামজীবনের ওই মধুর গল্পগুলি না লিখলে বিভূতিভূষণ জন্মাতেন কিনা সন্দেহ। আর ছবি আঁকলেন তাঁর সমকাল থেকে অনেক এগিয়ে। পল ভালেরির মতন দু- চারজন সাহেব ছাড়া তাঁর ছবির বিশেষ সমাদর করেনি কেউ, এখন দিনদিন তাঁর ছবি চিনতে শিখছেন সমঝদাররা।
মৃত্যুর বছরেও প্রুফ দেখতে দেখতে তিনি রানী চন্দকে একদিন বলেছিলেন, “এত লিখেছি জীবনে যে লজ্জা হয় আমার। এত লেখা উচিত হয়নি…জীবনের আশি বছর অবধি চাষ করেছি অনেক। সব ফসলই যে মড়াইতে জমা হবে তা বলতে পারিনে। কিছু ইঁদুরে খাবে। তবুও বাকি থাকবে কিছু। জোর করে কিছু বলা যায় না; যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছুই তো বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান, এটা জোর করে বলতে পারি।”
শেষ পর্যন্ত গান সম্পর্কে দুর্বলতা ছিল তাঁর। আজি হতে শতবর্ষ পরে কেউ তাঁর কবিতা আর পড়বে কিনা সে সম্পর্কে বিশ্বাস টলে গিয়েছিল? এত গদ্য লিখেছিলেন, ছেড়ে দিলেন তার সব দাবি? তিনি শুধু গানের স্রষ্টা? শুধু একজন গানের স্রষ্টাকে কি একজন বড় সাহিত্যিকের সম্মান দেওয়া যায় ?
মৃত্যুর বছরে তাঁর ওই দ্বিধা-আশঙ্কার কোনও ভিত্তি ছিল না। বেশি লিখেছেন তিনি ঠিকই, পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্যিক তাঁর সমতুল্য পৃষ্ঠা লিখে গেছেন কিনা সে বিষয়ে গবেষণার দরকার, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর উনসত্তর বছর পরেও বলা যায়, সাহিত্যের সবক’টি শাখায় বিচরণ করে তিনি একটা উঁচু মান তৈরি করে দিয়ে গেছেন। বাংলা ভাষাকে তিনি করে দিয়েছেন সর্বত্রগামী। যে কোনও ভাষায় এরকম একজন লেখকের আবির্ভাব প্রায় অলৌকিক ঘটনা ।
এখন মাঝে মাঝে ভাবি, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পুরোনো হয়ে গেছে। বড় বেশি কথার বাহুল্য, আর পড়বার দরকার নেই। তবু তাঁর দু-চারটি লাইন হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায়। এখনও পাতা ওলটাতে ওলটাতে তাঁর কোনও কোনও কবিতায় আবিষ্কারের আনন্দ পাই যেন। তখন মনে হয়, তাঁর পনেরোশো কবিতার মধ্যে বেছে এখনও একশো কবিতা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, যা আধুনিক পাঠককেও মুগ্ধ করতে পারে।
কিন্তু সেরকম সংকলন কোথায়? তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলি দ্বিতীয়বার পড়ার জন্য মনের মধ্যে কোনও তাগিদ অনুভব করি না। তা হলেও দৈবাৎ তাঁর কোনও ছোটগল্পের পৃষ্ঠায় চোখ আটকে গেলে, শুধু ভাসার সহাস্য মধুর দীপ্তির জন্যই শেষ না করে পারা যায় না। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসঙ্গীতও বেশ একঘেয়ে লাগে। মনে হয় ওই একই গান আর কতবার শুনব? তবু নিজের অজ্ঞাতসারেই যখন-তখন তাঁর গান দু-এক লাইন গেয়ে উঠি। কোনও প্রিয় গায়ক- গায়িকাকে গাইতে শুনলে ঠোঁট নড়ে। এক-একটা গান আচমকা বুকে ধাক্কা দেয়। গীতবিতানের পৃষ্ঠা উলটে একটা গান খুঁজতে গিয়ে তার পাশের গানটি এবং তারও পাশের গানটি চোখ টেনে রাখে।
মানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা যখনই ভাবি, তখন রামেন্দ্রসুন্দরেরই মতন, আমারও বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আবার চিঠিপত্রগুলি যখন পড়ি তখন ক্ষোভের সঙ্গে মনে হয়, এমন নিপুণভাবে তিনি আত্মগোপন করে থাকলেন কী করে? তাঁর এত অসংখ্য চিঠিতে, তাঁর কোনও জীবনীতেই তাঁকে চেনা যায় না। রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি চিনতে আমাদের আরও অনেকদিন লাগবে মনে হয় ।