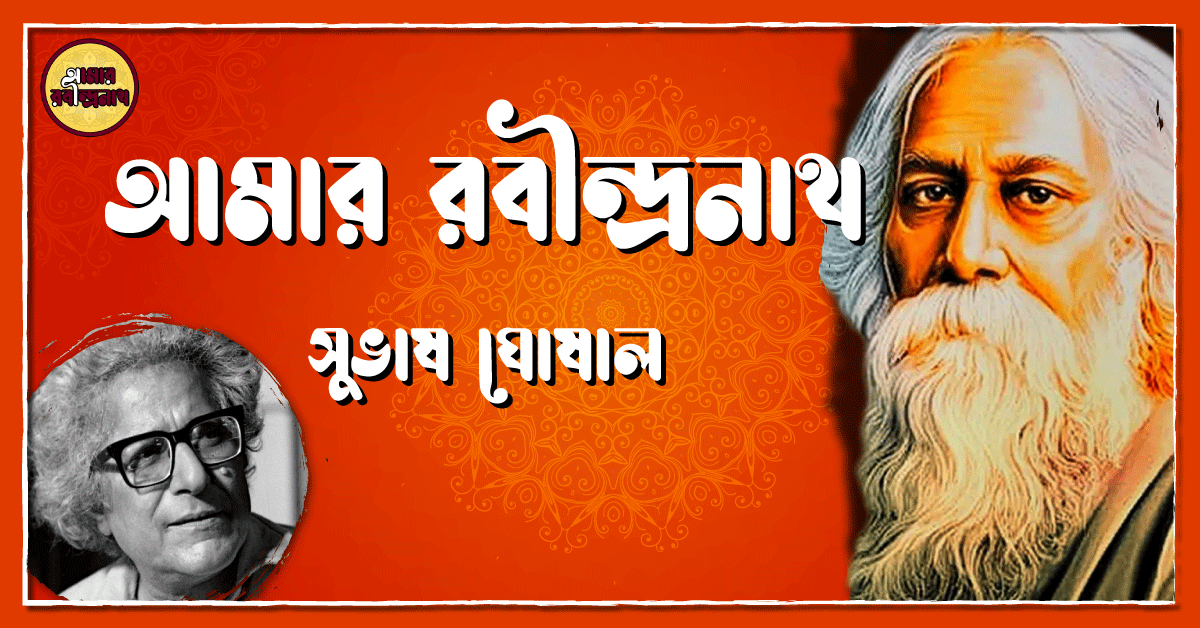প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সঙ্গীতশিল্পী ও সংগঠক সুভাষ ঘোষাল বাংলা গানের জগতে তাঁর স্বতন্ত্র স্বর ও গভীর অনুভবময় পরিবেশনার জন্য সুপরিচিত। রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক গান ও সৃষ্টিশীল সংগীতচর্চায় তাঁর অবদান দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে সমানভাবে সমাদৃত। সঙ্গীতচর্চার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞের আয়োজক হিসেবেও তিনি বাংলা সংস্কৃতির প্রসার ও সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন।
“আমার রবীন্দ্রনাথ” শিরোনামের নিবন্ধে সুভাষ ঘোষাল আন্তরিক ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও আত্মিক সম্পর্কের কথা। একজন শিল্পীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত, কবিতা ও ভাবনার প্রভাব, ব্যক্তিজীবনে এবং শিল্পীসত্তায় কীভাবে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, তা তিনি হৃদয়ের উষ্ণতায় প্রকাশ করেছেন। এই লেখাটি পাঠকের কাছে হয়ে উঠবে এক সঙ্গীতশিল্পীর অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথ-অনুভবের এক অন্তরঙ্গ দলিল।
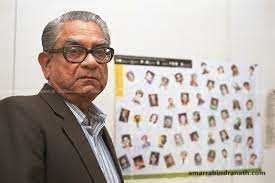
প্রথমেই একটা কথা ধ্বনিত এবং প্রতিধ্বনিত হোক—“যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক, তারা তো পারে না জানিতে—/ তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ আমার হৃদয়খানিতে।।” গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজো। রবীন্দ্রনাথের গান দিয়েই প্রকাশ করি তাঁর সার্ধশতবর্ষের প্রতি আমার একান্ত শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা আছে বলইে তাঁকে নিয়ে সংশয়ও জাগে নানারকম।
মাঝে মাঝে এ-দুঃখও হয়, কেন তিনি এত দেদীপ্যমানতার মধ্যেও বেশ ঝাপসা হয়ে আসেন কখনও কখনও। এই সংশয় আর দুঃখকে জড়ো করেই জ্বালিয়ে নেওয়া যায় অভিমানের একটা শিখা। বলাবাহুল্য, সেই শিখাও তাঁর স্মৃতির উদ্যাপনে আনন্দ-উৎসবের অন্তর্গত হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। এই বিশ্বাস আছে বলেই কিছু ভাবনা লিপিবদ্ধ করি নির্ভয়ে।
‘ধর্ম’ পর্যায়ের একটি লেখা ‘উৎসব’। রবীন্দ্র-নাথ লিখছেন, উদাসীনের নিকট একটা তৃণে কোনও আনন্দ নাই, তৃণ তাহার নিকট তুচ্ছ, তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু উদ্ভিবেত্তার নিকট তৃণের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে; কারণ, তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ব্যাপক, উদ্ভিদ পর্যায়ের মধ্যে তৃণের সত্য যে ক্ষুদ্রহ নহে, তাহা সে জানে। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিদ্বারা তৃণকে দেখিতে জানে তৃণের মধ্যে তাহার আনন্দ আরও পরিপূর্ণ—তাহার নিকট নিখিলের প্রকাশ এই তৃণের প্রকাশের মধ্যে প্রতিবিম্বিত।”
এই কথা যিনি লিখতে পারেন তিনি তো প্রকৃত অর্থে বলবান। সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে তাঁর অবস্থান। মন শান্ত হয়ে যায় তাঁর এই খণ্ডত্বের বিনাশবোধের আলোয়। কিন্তু সেই শান্তি স্থায়ী হয় না, টলে যায় অনতিবিলম্বে যদি নাগালের মধ্যে এসে পড়ে সরলা দেবী চৌধুরানির ‘জীবনের ঝরাপাতা’র একটি বিশেষ অংশ। সেই অংশে পরিষ্কার করে জানানো হয়েছে, “আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকের প্রথম ভাগ থেকে দশম একাদশ ভাগ পর্যন্ত যত দূর ছাপানো হয়েছে সগুণ সাকার ঈশ্বরভাবের সব রকম সঙ্গীত স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে।
ভাবের ও ভাষার পার্থক্য দেখলে চিনতে পারা যাবে রামমোহন রায়ের সময়কার নিরাকার ব্রহ্ম কেমন করে ভাবের ঘরে একদম সাকার হয়ে নেমে ব্রহ্মবাদীর আকার-নিরাকার অভেদ জ্ঞানের ভিত্তিই পুনঃস্থাপিত করলেন। অথচ ভাবের ছবির চৌকাঠ পেরিয়ে গেলেই—মাটি-খড়ে, ধাতু-প্রস্তরে বর্ণে-চিত্রে ভাবের উপলক্ষ্য ভগবানকে পূর্ণ লক্ষ্য করে মূর্ত করে আঁকড়ে ধরলেই রবীন্দ্র-নাথ উত্যক্ত বিচলিত হয়ে উঠতেন। তাঁর আজন্ম ‘নিরাকার’ পূজার সংস্কারে ঘা লাগত।” এও শুনেছি, সরলারা কালীঘাট মন্দিরে আসতে চাইলে বাধা দিতেন রবীন্দ্র-নাথ।
তিনি তো নিজেই স্বীকার করেছেন অবস্থান বিশেষে তৃণের মধ্যে নিখিলের বিকাশ সম্ভব। তাই যদি হয়, তবে মূর্তির মধ্যে নিখিলের প্রকাশ প্রকৃত ভক্তের চোখে সম্ভব হবে না কেন? রাবীন্দ্রিক অসহিষ্ণুতা অন্তত এই ক্ষেত্রে প্রশ্নটিকে সতেজ করে তোলে। কিন্তু এই প্রশ্নের নির্ভরযোগ্য কোনও উত্তর রবীন্দ্র-নাথ উপহার দিতে পেরেছিলেন কি না জানি না। ফলে আমার মনে একটা নতুন জিজ্ঞাসার জন্ম হয়। উৎকর্ণ হয়েও সারাক্ষণ, তিনি কি উদাসীন ছিলেন কখনও কখনও? তাঁর মতো এত বড় মাপের জাগরণ কী করে ক্ষুণ্ণ হয় মতবাদের নিদ্রা দ্বারা যে কোনও মুহূর্তে?
রবীন্দ্র-নাথকে সাম্প্রদায়িক বলার মতো মূর্খতা ক’জনের আছে জানি না। সম্প্রদায়-নির্বিশেষে মানুষ তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে খুঁজে পেয়েছে বেঁচে থাকার গ্লানির হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সাহস। সবকিছু ভুলে থাকলেও তাঁর গান ভুলে থাকার উপায় নেই বিন্দুমাত্র। যাঁরা বাংলাভাষী, তাঁরা যে ধর্মেরই হোন না কেন, তাঁদের দৈনন্দিতা বা তাঁদের প্রাত্যহিকতার মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত কোনও না কোনও সময় লাবণ্যনির্ঝর হয়ে নেমে আসবেই।
কিন্তু ‘গীতবিতান’ হাতে তুলে নিয়ে যখন আপনমনে ভাবার সুযোগ পাই তখন লক্ষ করি, শত শত ঋদ্ধি ও সিদ্ধি আছে, আছে পুজো, প্রেম, স্বদেশ, প্রকৃতি এবং বিচিত্রের কতরকম দোলা, কিন্তু কী একটা যেন নেই যার অভাবের জোরটা মাঝে মাঝে অনুভব করা যায়। তাঁর গানের মধ্যে অনন্তকে কত রঙে-রেখায় এমনকী গার্হস্থ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হলেও একটা আলপনার অনুপস্থিতি বেদনার সৃষ্টি করে।
মৃন্ময়কে অবলম্বন করে চিন্ময়ের জন্য যে কান্না তা কেন এল না রবীন্দ্রসঙ্গীতে! বাংলার নিজস্ব যে মাতৃসঙ্গীত আবহমানতার দ্বারা পূর্ণ হয়ে আছে, যেখানে মৃন্ময়ীকে ঘিরে চিন্ময়ীর জন্য ঝরানো হয়েছে মর্মাশ্রু, সেই মাতৃসঙ্গীত থেকে থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন রবীন্দ্রনাথ! যাঁর কলম থেকে এত সব ভাবের দ্যোতনা নেমে এসেছে, তাঁর কলম থেকে কেন বেরলো না এমন মাতৃসঙ্গীত যা স্বদেশের নয়, সত্তায় পুরোপুরি ! অথচ নজরুল ইসলাম কিন্তু পেরেছিলেন। স্বদেশের জন্য গান বেঁধেও মাতৃপুজোর জন্য গান বাঁধার দ্বিধা জয় করতে পেরেছিলেন সহজে এবং আনন্দের সঙ্গে। কেন এমন হল?
রবীন্দ্রনাথের যে লেখাটি আজও যখন পড়ি রোমাঞ্চিত হই, সেই লেখাটিতে জ্যাঠামশায়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস এই চারজনকে চার অংশ বলে মনে হয় না। বরং মনে হয়, কবিতা, গান, ছবি ও ধর্ম রবীন্দ্রনাথের এই চারটি দিক মিলেই ‘চতুরঙ্গ’ হয়েছে। তাঁর বিপুল সৃষ্টির আর কোনও লেখায় এত ঘনত্ব নিয়ে এতখানি সমন্বয় পাওয়া গিয়েছে কি না সন্দেহ। তাঁর ধর্মে ব্রহ্ম নিরাকার, কিন্তু প্রেম সাকার । যা নিরাকার তার বিপুল চাপ থেকেই জন্ম নিয়েছে সেই সাকারত্ব যা ধারণ করতে পেরেছে দামিনী।
আর দামিনীকে ধারণ করার জন্য প্রয়োজন হয়েছে কবিতা, গান, ছবি ও তাঁর ধর্মের ছত্রছায়া। শ্রীবিলাস সেখানে একটি অসহায় সাক্ষী মাত্র। এই লেখার বিভিন্ন জায়গায় জ্যাঠামশায়ের মুসলমানপাড়ার দল এসে বিশেষ ভূমিকা পালন করে গিয়েছে। দামিনী ও শ্রীবিলাসের বিয়েতে তাদের আনন্দকলরব ভেঙে দিয়েছে অবাঞ্ছিত নীরবতা। শচীশ নতুন দম্পতিকে তাদের বাড়িটা ভোগ করতে বলেছিল। কিন্তু সে বাড়ি তখন হরিমোহনের নাগপাশে। “বাড়িটা কেমন করিয়া হরিমোহনের হাত হইতে উদ্ধার করা গেল সে অনেক কথা। আমার প্রধান সহায় ছিল পাড়ার মুসলমানরা। আর কিছু নয়, জগমোহনের উইলখানা একবার তাদের দেখাইয়াছিলাম। আমাকে আর উকিলবাড়ি হাঁটাহাঁটি করিতে হয় নাই।”
বাইরে যখন শ্রীবিলাসের কাজ আর ভিতরে দামিনীর, যখন মিশে যাচ্ছে গঙ্গাযমুনার স্রোত, তখনও জানিতে দেওয়া হচ্ছে, “ইহার উপরে দামিনী পাড়ার ছোট ছোট মুসলমান মেয়েদের সেলাই শেখাইতে লাগিয়া গেল। কিছুতেই সে আমার কাছে হার মানিবে না, এই তার পণ।” সেলাই শেখানোর মধ্যে শুধু সমাজ সেবার তাৎপর্য নেই, আরও এক ভিন্নতর তাৎপর্য খুঁজে পাই। দুটি সম্প্রদায়ের পুণ্য বন্ধনের মধ্যে যে সব জায়গা জোড়া লাগেনি, অথবা ছিঁড়ে গিয়েছে যে সব জায়গা, সে সব জায়গা মেরামত করার দায়িত্ব এসে পড়েছে, ‘সেই তুমি’ আর ‘এই তুমি’র মাঝখানের ঘোরটা যে পেরিয়ে আসতে পেরেছে সদ্য, সেই দামিনীরই উপর।
এতটাই ঔদার্য এবং চিন্তাশীলতা আমি পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। তবে কেন “মাটি-খড়ে, ধাতু- প্রস্তরে, বর্ণে-চিত্রে ভাবের উপলক্ষ্য ভগবানকে পূর্ণ লক্ষ্য করে মূর্ত করে আঁকড়ে ধরলেই রবীন্দ্রনাথ উত্যক্ত বিচলিত হয়ে উঠতেন?” কেন তিনি নিরাকার এবং সাকার এই দুটি অবস্থানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উঠতে পারলেন না? দামিনীর সেলাইকলের কথা কেন ভুলে গেলেন তারই স্রষ্টা? তবে কি তাঁর ধর্মবোধের মধ্যে অসঙ্গতির মতো একটা কিছু মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছিল তাঁর সমুন্নত মস্তকের মহত্ব সত্ত্বেও ?
আসলে তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে দিয়ে অতি সন্তর্পণে এগোলে মনে হতে থাকে, তাঁর ধর্মবোধের মধ্যে মানবিকতার রং এত বেশি পরিমাণে জড়িয়ে গিয়েছে যে, কখনও কখনও তাঁকে প্রবুদ্ধ না বলে প্রশিক্ষক বললে ঠিক বলা হয়। তিনি তাঁর ধর্মবিশ্বাসকে যতটা তত্ত্বগত দিক থেকে লাভ করেছিলেন ততটা কি লাভ করেছিলেন আত্মগত দিক থেকে, এমন সংশয় আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর একটা কথাও এই সুযোগে বলে নিই। আমাদের মধ্যে এমন অনেক ড্রয়িংরুমশাণিত পণ্ডিত আছেন, যাঁরা আজও ধর্মের সঙ্গে আধ্যাত্মকে একাকার করে দিয়ে অবান্তর কথা বলার প্রায় একটা ঘরাণা তৈরি করে ফেলেছেন। অথচ ধর্মের সঙ্গে আধ্যাত্মের অবস্থানগত পার্থক্য এতটাই যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।
রবীন্দ্রনাথের মানবিকতার বোধ এবং তাঁর ধর্মবোধ নিকটতম প্রতিবেশী হলেও তিনি যে সেই জোরে আধ্যাত্মের উপলব্ধিতে পৌঁছে সেখানে লাভ করেছিলেন একটি ভূখণ্ড, এমন কথা বললে বোধহয় সত্যেরই অপলাপ হবে। “আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ। সুরের বাঁধনে/তুমি জানো না, আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে।” এই ‘অজানা সাধন’-এর বিভূতিরূপে যা এসেছে তা দিয়ে আমাদের ছোট ছোট ঝুলি ভরে উঠেছে অনেক সময়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সেই পূর্ণতায় আধ্যাত্মের পরিমাণ বলার মতো।
সম্প্রতি হাসান ফেরদৌস তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথ, শিকাগোর কবিতা পত্রিকা ও মিসেস মুডি’ নামক প্রবন্ধের এক জায়গায় বলছেন, “রবীন্দ্রনাথকে যে পশ্চিমে প্রধানত একজন ধর্মগুরু হিসেবে দেখা হয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই সম্ভবত সেই চিত্রটি তাঁর শ্রোতা-দর্শকদের মনে এঁকে দিয়েছিলেন।…তাঁর বিলাতে অবস্থানকালে যে ক’জন ইংরেজ পণ্ডিত ও কাব্যরসিকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় হয়, তাঁদের অনেকেই তাঁকে একজন প্রাচ্যদেশীয় সাধু বিবেচনা করে সালাম ঠুকেছেন বা সম্মানিত দূরত্ব রক্ষা করে চলেছেন।
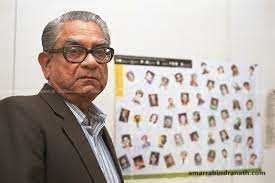
এমনকী ইয়েটস, যিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একাধিকবার দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ পান, তাঁর কাছেও রবীন্দ্র-নাথের এই সন্তের ইমেজটিই সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে। রোটেনস্টাইন, যাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সখ্য সিকি শতাব্দীর বেশি, তিনিও বারবার রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতায় তাঁর বিমুগ্ধতার কথা স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই সন্ত-সুলভ ইমেজ ইংরেজদের মনে এমন তীব্রভাবে ধরা ছিল যে, ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের লন্ডন ভ্রমণকালে সাবেক ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য স্টাফোর্ড ব্রুক রবীন্দ্রনাথকে নিজ গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করার সময়ে রোটেনস্টাইনকে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন কবিকে জানিয়ে দেন তিনি (অর্থাৎ ব্রুক) মোটেই আধ্যাত্মিক কোনও মানুষ নন।” এই উদ্ধৃতির মধ্যেও ধর্ম ও আধ্যাত্মকে একাসনে বসানোর একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। একজন ধর্মগুরুর সঙ্গে একজন অধ্যাত্মপথের অভিযাত্রীর ফারাকটা বড় বেশি!
১৯৩৬-এর সেপ্টেম্বরে, অর্থাৎ প্রয়াত হওয়ার প্রায় পাঁচবছর আগে দিলীপকুমার রায়কে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর অন্তরকে মেলে ধরেছেন। “বিশ্বাস করো বা না করো আমি নিজেকে কখনওই সাধক বলে কল্পনা করিনে। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে আমার অধিকার নেই একথা আমি নিশ্চিত জানি এবং কাউকেই আমি ভুল জানাই নে। আমার জীবনে যা কিছু অভিজ্ঞতা তা কবি প্রকৃতির অভিজ্ঞতা। তার উর্ধ্বেরও উপলব্ধির ক্ষেত্র আছে কিন্তু সেখানে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান পৌঁছয় না। আমার মন প্রকাশের appearance-এর সীমার মধ্যেই সঞ্চরণ করে, আনন্দ পায়।”
পূর্ব বাংলার গৌরীপুরের জমিদার ও সরোদিয়া বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৯৩৪-এর কোনও এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে জানতে পারেন, তাঁর ধর্মবিশ্বাস ব্রাহ্মধর্মের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হওয়ায় দেবদেবীদের মণ্ডল নিয়ে কিছু মানতে তিনি নারাজ। সেই কথা বীরেন্দ্রকিশোরের বন্ধু দিলীপকুমার শ্রীঅরবিন্দকে জানালে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেন তা ইঙ্গিতবাহী—আমার মনে হয় না যে রবীন্দ্রনাথ নাস্তিক।
ব্রাহ্ম প্রভাব এবং নিরাকার ব্রহ্মের ব্যাপারটাকে নাস্তিকতা বলা যাবে না। তবে আমার মনে হয় তাঁর বিশ্বাসের জায়গাগুলো পলকা, নির্দিষ্ট কিছু নয়। তাঁর যেটা আদর্শবাদ সেটা নিছকই আদর্শবাদ। তা শরীর ও আত্মার পক্ষে ভালো হলেও তার সম্ভাব্যতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আশানুরূপ নয়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমার অভিমানটা এখানেই। যিনি এত ব্যাপকভাবে সুন্দরের রাজ্যে নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছেন, তিনি কেন তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার সম্বল সত্ত্বেও সংস্কারের সংসারের জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পারলেন না শেষপর্যন্ত ?
যিনি জ্যোতির্ময়ের হাতে নবীন আশার খড়্গ দেখতে পেয়েছিলেন, যিনি বলতে পেরেছিলেন, “জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে, বন্ধন হোক ক্ষয়।” তাঁর খড়া কেন নেমে এল না যথাসময়ে ?