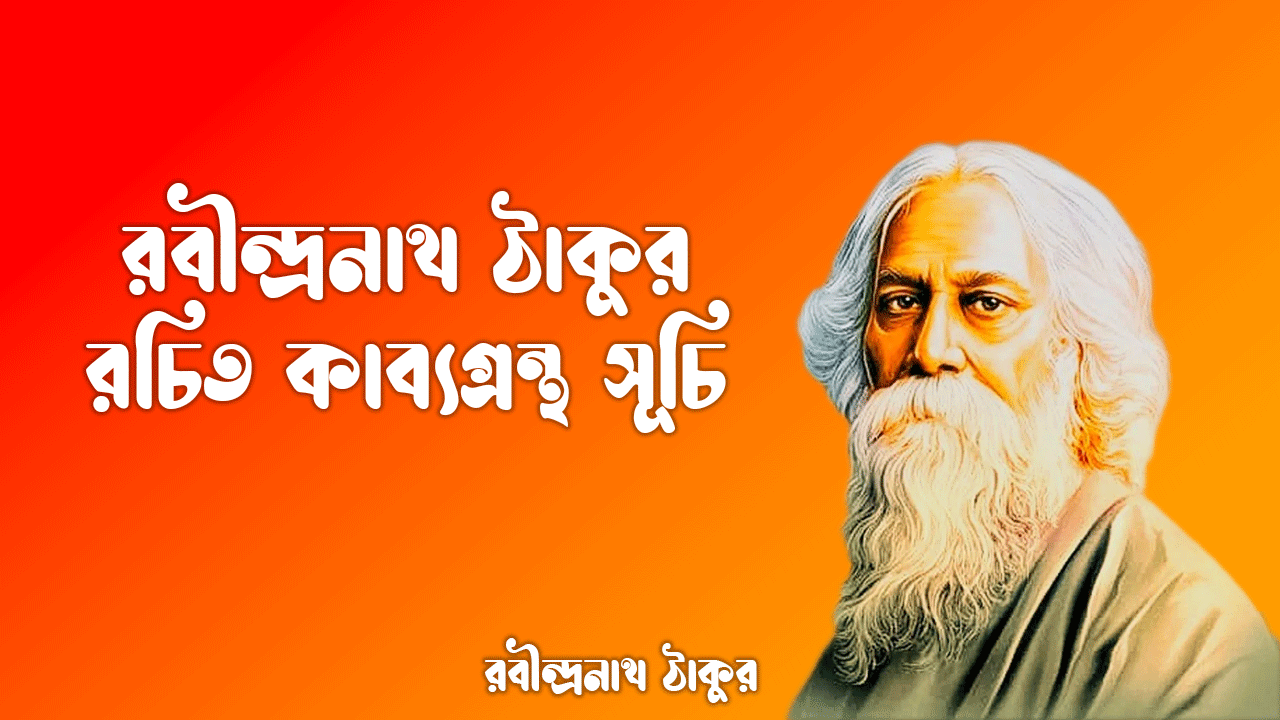রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের এক অমর প্রতিভা, যিনি কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটকসহ সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় রেখেছেন অনন্য অবদান। তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহ বাংলা কাব্যসাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। প্রকৃতি, প্রেম, মানবতা, দর্শন, দেশপ্রেম ও আধ্যাত্মিকতা—এইসব বিষয় তাঁর কবিতার মূল সুর। ‘সোনার তরী’, ‘ছবির দেশ’, ‘মানসী’, ‘গীতাঞ্জলি’, ‘গীতিমাল্য’, ‘ক্ষণিকা’, ‘বলাকা’, ‘পুনশ্চ’, ‘শেষ লেখা’ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তাঁর কাব্যপ্রতিভার গভীরতা ও বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়েছে। এসব সৃষ্টিকর্ম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি বিশ্বসাহিত্যে বাঙালি কবিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে এক বিশ্বকবির আসনে।
Table of Contents
প্রারম্ভিক জীবন ও প্রথম পর্যায়
রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থসমূহ সাহিত্য সমালোচনায় বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫–১৮৯৪)-এর প্রভাবাধীন। তাঁর কবি-কাহিনী, বনফুল ও ভগ্নহৃদয় কাব্যগ্রন্থে বিহারীলালের রোমান্টিকতা ও ভাবধারার স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়।
দ্বিতীয় পর্যায় – আত্মপ্রকাশের সূচনা
‘সন্ধ্যাসংগীত’ কাব্যগ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজের স্বকীয় কণ্ঠস্বর খুঁজে পান। এই পর্যায়ের সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল মানব হৃদয়ের বিষণ্ণতা, আনন্দ, মর্ত্যপ্রীতি ও মানবপ্রেম।
১৮৯০–১৯০০ সময়কালে প্রকাশিত মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালি (১৮৯৬), কল্পনা (১৯০০) ও ক্ষণিকা (১৯০০) কাব্যে প্রেম, সৌন্দর্য ও রোম্যান্টিক চিন্তার উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটে।
তৃতীয় পর্যায় – আধ্যাত্মিকতার উত্থান
১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আধ্যাত্মিক ভাবনার প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এ সময়কার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য — নৈবেদ্য (১৯০১), খেয়া (১৯০৬), গীতাঞ্জলি (১৯১০), গীতিমাল্য (১৯১৪) ও গীতালি (১৯১৪)।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আধ্যাত্মিক ভাবনার পরিবর্তে আবার মানবজীবনের বাস্তব দিকের প্রতি মনোযোগী হন। বলাকা (১৯১৬)-তে এ মনোভাব প্রতিফলিত হয়। পরে পলাতকা (১৯১৮)-তে গল্প-কবিতার আকারে সমকালীন নারীজীবনের সমস্যাগুলি ফুটে ওঠে।
চতুর্থ পর্যায় – প্রেমে প্রত্যাবর্তন ও নতুন ধারা
১৯২০-এর দশকে রবীন্দ্রনাথ আবার প্রেমকে উপজীব্য করেন। পূরবী (১৯২৫) ও মহুয়া (১৯২৯)-তে এ রোমান্টিক ভাবনা নতুন রূপ পায়। এর পরপরই প্রকাশিত হয় চারটি গদ্যকাব্য — পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), পত্রপুট (১৯৩৬) ও শ্যামলী (১৯৩৬)।
শেষ দশকের সৃজন ও পরীক্ষানিরীক্ষা
জীবনের অন্তিম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতার আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর উপর নতুন ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা চালান। রোগশয্যায় থেকেও তিনি সৃষ্টি করেন গভীর জীবনদর্শনসমৃদ্ধ কাব্যগ্রন্থ — রোগশয্যা (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিনে (১৯৪১) ও শেষ লেখা (১৯৪১, মরণোত্তর প্রকাশিত)। এইসব রচনায় মৃত্যু, জীবনপ্রেম ও অনন্ততার প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে। মৃত্যুর মাত্র আট দিন আগে তিনি মৌখিকভাবে রচনা করেন তাঁর শেষ কবিতা — “তোমার সৃষ্টির পথ”।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কাব্যগ্রন্থ:
প্রারম্ভিক জীবন ও প্রথম পর্যায়
পর্যায় অনুসারে তাঁর রচিত কাব্য গ্রন্থের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হল –
১। কবি কাহিনী (১৮৭৮)
কবি-কাহিনী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ, যা ১৮৭৮ সালের ৫ নভেম্বর তাঁর মাত্র ষোলো বছর বয়সে প্রকাশিত হয়। যদিও বনফুল কাব্যগ্রন্থ পূর্বে রচিত, প্রকাশের দিক থেকে এটি তাঁর প্রথম গ্রন্থ। বইটিতে ৫৩ পৃষ্ঠা এবং এর কবিতাগুলি প্রথমে ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এতে বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রভাব স্পষ্ট। গ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন কবির বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রার আগে এটি মুদ্রিত দেখতে পাননি। কবি-কাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন …
২। বনফুল (১৮৮০)
বনফুল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি বাংলা কাব্যগ্রন্থ, যা ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হয়। আটটি সর্গে বিভক্ত এই গ্রন্থে বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার “সূচনা পর্ব”-এর অন্তর্গত প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ। রচনার ক্ষেত্রে বনফুল কবি-কাহিনী-এর পূর্ববর্তী হলেও, প্রকাশের দিক থেকে কবি-কাহিনী (১৮৭৮) প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। বনফুল এর বিস্তারিত দেখুন ..
৩। ভগ্নহৃদয় (১৮৮১)
ভগ্নহৃদয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বাংলা কাব্যগ্রন্থ, যা ১৮৮১ সালে প্রকাশিত হয়। এটি মোট ৩৪টি সর্গে বিভক্ত। রবীন্দ্রনাথ লন্ডন ভ্রমণকালে এই কাব্যের রচনা শুরু করেছিলেন এবং পরবর্তীতে দেশে ফিরে তা সম্পূর্ণ করেন। গ্রন্থটিতে মূলত প্রেম, বেদনা ও মানবমনের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। কাব্যের ভাষা ও ভাবধারায় সেই সময়কার তাঁর কাব্যচর্চার সূক্ষ্ম রোমান্টিক প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যা বাংলা কাব্যসাহিত্যে তাঁর প্রাথমিক সৃষ্টিশীল পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। ভগ্নহৃদয় সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন ….
উন্মেষ পর্যায় (১৮৮২ – ১৮৮৬) :
১। সন্ধ্যা সঙ্গীত (১৮৮২)
সন্ধ্যা সঙ্গীত তাঁর কাব্য রচনার “উন্মেষ পর্ব”-এর অন্তর্গত। কাব্যের প্রকাশকাল বাংলা ১২৮৮ সন (ইংরেজি ১৮৮২ সাল)। তবে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, “গ্রন্থে ১২৮৮ মুদ্রিত হলেও, কার্যতঃ ১২৮৯ সালে প্রকাশিত।” প্রথমে এই কাব্যে পঁচিশটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে তিনটি বাদ দেওয়া হয়েছিল। সমালোচক শিশিরকুমার দাশ এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি সম্পর্কে লিখেছেন, “এদের মূল সুর বিষাদের, রোম্যান্টিক বেদনা ও শূন্যতাবোধের। এই কবিতাগুলির মধ্যে বাংলা কবিতার এক নূতনধারার সূচনা হয়েছিল।” সন্ধ্যা সঙ্গীত এর বিস্তারিত দেখুন ….
২। প্রভাত সঙ্গীত (১৮৮৩)
প্রভাত সংগীত ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থের নাম ছিল সন্ধ্যা সঙ্গীত (১৮৮২)। কাব্যগ্রন্থটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবি জীবনের দ্বিতীয় ধাপের সমাপ্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রভাত সংগীত এর বিস্তারিত দেখুন ….
৩। শৈশব সঙ্গীত (১৮৮৪)
শৈশব সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লেখেন – এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম, সুতরাং ইহাকে ঠিক শৈশবসঙ্গীত বলা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু নামের জন্য বেশী কিছু আসে যায় না। কবিতা গুলির স্থানে স্থানে অনেকটা পরিত্যাগ করিয়াছি, সাধারণের পাঠ্য হইবে না বিবেচনায় ছাপাই নাই। হয়ত বা এই গ্রন্থে এমন অনেক কবিতা ছাপা হইয়া থাকিবে যাহা ঠিক প্রকাশের যোগ্য নহে। কিন্তু লেখকের পক্ষে নিজের লেখা ঠিকটি বুঝিয়া উঠা অসম্ভব ব্যাপার—বিশেষতঃ বাল্যকালের লেখার উপর কেমন-একটু বিশেষ মায়া থাকে যাহাতে কতকটা অন্ধ করিয়া রাখে। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি আমি যাহার বিশেষ কিছু না-কিছু গুণ না দেখিতে পাইয়াছি তাহা ছাপাই নাই। শৈশব সঙ্গীত এর বিস্তারিত দেখুন ….
৪। ছবি ও গান (১৮৮৪)
ছবি ও গান হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক রচিত একটি বাংলা কাব্যগ্রন্থ। এটি ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনার “উন্মেষ পর্ব”-এর অন্তর্গত। মানবজীবনের হাসিকান্নার কাহিনী এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য বিষয়। ছবি ও গান এর বিস্তারিত দেখুন ….
৫। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪)
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ব্রজবুলি ভাষায় রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ কৈশোর ও প্রথম যৌবনে “ভানুসিংহ ঠাকুর ” ছদ্মনামে বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে কিছু পদ রচনা করেছিলেন। ১৮৮৪ সালে সেই কবিতাগুলিই ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী নামে প্রকাশিত হয়। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী এর বিস্তারিত দেখুন ….
৬। কড়ি ও কোমল
কড়ি ও কোমল হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক রচিত একটি বাংলা কাব্যগ্রন্থ। এটি ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনার “উন্মেষ পর্ব”-এর অন্তর্গত একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। কড়ি ও কোমল এর বিস্তারিত দেখুন ….
ঐশ্বর্য পর্ব (১৮৯০ – ১৯০০) :
১। মানসী ১৮৯০:
মানসী হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক রচিত একটি বাংলা কাব্যগ্রন্থ। এটি ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনার “মানসী-সোনার তরী পর্ব”-এর অন্তর্গত একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। বীন্দ্রনাথ একজন ভ্রমণকারীও ছিলেন। গাজীপুরে থাকাকালীন সময়ে তিনি “মানসী”-এর বেশিরভাগ কবিতা লেখেন। সেখানকার অনুপম প্রাকৃতিক পরিবেশ কবিকে ছন্দোবদ্ধ কবিতাগুলি লেখতে সহায়তা করে। এটি ছিল তাঁর প্রথম পরিপক্ব গ্রন্থ যেখানে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রকার ছন্দ নিয়ে গবেষণা করেন। মানসী এর বিস্তারিত দেখুন ….
২। সোনার তরী ১৮৯৪:
সোনার তরী হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক রচিত একটি বিখ্যাত বাংলা কাব্যগ্রন্থ। সমগ্র গ্রন্থটি বাংলা কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক কাব্য সংকলন। এটি ১৮৯৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনার “মানসী-সোনার তরী পর্ব”-এর অন্তর্গত একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। সোনার তরী এর বিস্তারিত দেখুন ….
৩ নদী ১৮৯৬
নদী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বাংলা কাব্যগ্রন্থ, যা ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। এতে প্রকৃতি, বিশেষ করে নদী ও তার আশেপাশের জীবনের সৌন্দর্য, গতি ও বৈচিত্র্য কবিতার মাধ্যমে গভীরভাবে ফুটে উঠেছে।
৪ চিত্রা ১৮৯৬
চিত্রা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ, যা ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর কাব্যসৃষ্টির রোমান্টিক পর্যায়ের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। গ্রন্থটিতে প্রকৃতি, প্রেম ও সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম প্রকাশ কবিতার বুননে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ‘চিত্রা’ মূলত তাঁর কল্পনাশক্তি ও চিত্রধর্মী বর্ণনার জন্য সমাদৃত, যেখানে শব্দের মাধ্যমে রঙ, আলো-ছায়া ও আবেগের এক অনন্য শিল্পরূপ ফুটে ওঠে। এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক, প্রেমের নানান স্তর এবং অন্তর্লোকের অনুভূতি গভীরভাবে ধরা পড়েছে। বাংলা কাব্যসাহিত্যে ‘চিত্রা’ তার স্নিগ্ধতা ও নান্দনিকতার জন্য স্থায়ী স্থান করে নিয়েছে।
৫ চৈতালী ১৮৯৬
চৈতালী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ, যা ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বসন্ত ও গ্রীষ্মের সন্ধিক্ষণ—বাংলার চৈত্র মাসের প্রকৃতি, রূপ ও আবহ—কাব্যময়ভাবে ধরা পড়েছে। কবিতাগুলিতে গ্রামীণ জীবনের সরলতা, কৃষকের পরিশ্রম, ফসল তোলার আনন্দ ও ঋতুর পরিবর্তনের সজীব চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রকৃতি এখানে শুধু পটভূমি নয়, বরং কবির ভাবনা ও আবেগের অংশীদার। ‘চৈতালী’ গ্রন্থের ভাষা স্নিগ্ধ, চিত্রময় এবং সংগীতধর্মী, যা পাঠককে বাংলা গ্রামাঞ্চলের জীবন্ত অনুভূতির ভেতর টেনে নিয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যে এটি ঋতুকেন্দ্রিক কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
৬ কণিকা
কণিকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ, যা ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মূলত সংক্ষিপ্ত আকারের দার্শনিক ও চিন্তাপ্রবণ কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে, যা তাঁর গভীর মনন ও অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। ‘কণিকা’ শব্দের অর্থই ইঙ্গিত দেয় ক্ষুদ্র অথচ তাৎপর্যময় সৃষ্টিকে—প্রতিটি কবিতা যেন ছোট ছোট মুক্তোর দানার মতো, যেখানে জীবনের বিভিন্ন দিক, মানবপ্রেম, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা ও আত্মসমালোচনার ভাব গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সরল অথচ গভীর বাকভঙ্গি, লঘু ছন্দ ও গাঢ় অনুভূতি এই গ্রন্থকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। বাংলা কাব্যসাহিত্যে এটি সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ কবিতার এক অনন্য সংকলন।
৭ কথা ও কাহিনী
কথা ও কাহিনী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ, যা ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে কবি নানা রকম ভাবপ্রবণ ও কাহিনীনির্ভর কবিতা সংকলন করেছেন, যেখানে প্রেম, প্রকৃতি, মানবজীবনের দ্বন্দ্ব, ঐতিহাসিক ঘটনা ও লোককথার অনুষঙ্গ মিশে আছে। প্রতিটি কবিতায় বর্ণনাধর্মী আঙ্গিকের পাশাপাশি রয়েছে গভীর কাব্যিক সৌন্দর্য ও আবেগের প্রবাহ। ভাষা ও ছন্দের মাধুর্য, চিত্রকল্পের সজীবতা এবং ভাবের গভীরতা গ্রন্থটিকে পাঠকের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত করেছে। কথা ও কাহিনী রবীন্দ্রনাথের সেই সময়কার সৃষ্টিশীলতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন, যা বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে এবং গল্পধর্মী কবিতার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।
৮ কল্পনা
কল্পনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ, যা ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয়। এতে মোট ৪২টি কবিতা সংকলিত হয়েছে, যেখানে কবি প্রেম, প্রকৃতি, মানবিক অনুভূতি, দার্শনিক ভাবনা ও জীবনের নান্দনিক দিককে কাব্যিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটির নামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রতিটি কবিতায় কল্পনার সৃজনশীল বিস্তার ও চিত্রধর্মী বর্ণনা ফুটে উঠেছে। ভাষার সুষমা, ছন্দের মাধুর্য এবং ভাবপ্রকাশের গভীরতা পাঠককে মুগ্ধ করে। কল্পনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যপর্বের কাব্যসৃজনের অন্যতম নিদর্শন, যা বাংলা সাহিত্যে কল্পনাপ্রবণ রচনার এক উজ্জ্বল সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হয়।
৯ ক্ষণিকা
ক্ষণিকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কাব্যগ্রন্থ, যা ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মোট ৫৪টি ছোট ছোট কবিতা সংকলিত হয়েছে, যেখানে মুহূর্তের অনুভূতি, ক্ষণস্থায়ী ভাবনা ও হঠাৎ উদ্ভূত আবেগকে কাব্যিক রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কবিতাই সংক্ষিপ্ত হলেও ভাবপ্রকাশে গভীর এবং আবেগঘন। প্রেম, প্রকৃতি, জীবন ও দার্শনিক চিন্তা—সবই এখানে ক্ষণিক আবহে ধরা দিয়েছে। ভাষার সংযম, ছন্দের লঘুতা ও ভাবের তীব্রতা ক্ষণিকাকে বাংলা সাহিত্যে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। এটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল দিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।
অন্তবর্তী পর্ব (১৯০১ – ১৯২৯) :
১ নৈবেদ্য
নৈবেদ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কাব্যগ্রন্থ, যা ১৯০১ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনা, ভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেম প্রধান বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে আধ্যাত্মিকতার স্রোত প্রবল হয়, নৈবেদ্য তার অন্যতম প্রথম প্রকাশ। কবিতাগুলিতে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ, জীবনের ক্ষুদ্রতা ও মহত্ত্বের অনুভব, এবং মানুষের অন্তর্গত সাধনার কথা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ভাষা ও ছন্দে সহজতা বজায় রেখে তিনি ভক্তিমূলক কাব্যের এক অনন্য ধারা নির্মাণ করেছেন, যা পাঠকের মনে শান্তি ও অনুপ্রেরণা জাগায়।
২ স্মরণ
স্মরণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কাব্যগ্রন্থ, যা ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয়। এটি মূলত স্মৃতিচারণা ও গভীর আবেগের সমন্বয়ে রচিত, যেখানে ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা, হারানো মানুষের প্রতি মমতা এবং অতীতের স্মৃতির টান প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে এক ধরনের কোমল বিষাদ ও আত্মমগ্নতার সুর প্রতিফলিত হয়েছে, যা পাঠককে গভীর ভাবনায় নিমগ্ন করে। ভাষা সহজ, কিন্তু অনুভূতির গভীরতা তীক্ষ্ণ ও স্পর্শকাতর। স্মরণ কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখী ভাবনার এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত, যা তাঁর সাহিত্যিক সৃষ্টিতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।
৩ শিশু
শিশু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ, যা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে। এই গ্রন্থে মূলত শিশুদের জন্য রচিত কবিতা অন্তর্ভুক্ত হলেও, এর ভাষা, ছন্দ ও ভাবনার গভীরতা প্রাপ্তবয়স্ক পাঠককেও সমানভাবে আকৃষ্ট করে। কবিতাগুলিতে শৈশবের সরলতা, আনন্দ, কল্পনার জগৎ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মেলবন্ধন ঘটেছে। গ্রন্থে “সাত ভাই চম্পা”, “শীতের বিদায়”, “সমালোচক” প্রভৃতি চিরকালীন জনপ্রিয় কবিতা স্থান পেয়েছে। সহজ-সরল শব্দচয়ন, ছন্দের মাধুর্য ও চিত্রকল্পের জীবন্ত ব্যবহার শিশু কাব্যগ্রন্থকে বাংলা শিশু-কাব্যের এক অনন্য নিদর্শন করেছে, যা আজও সমানভাবে পাঠকপ্রিয়।
৪ উৎসর্গ
উৎসর্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কাব্যগ্রন্থ, যা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। এই গ্রন্থে কবি গভীর আবেগ, ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং আত্মসমর্পণের ভাবনা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। উৎসর্গ নামটি থেকেই বোঝা যায়, এখানে কবি তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থ অনুভূতি, কৃতজ্ঞতা ও প্রেম নিবেদন করেছেন এক বিশেষ ব্যক্তিকে বা প্রতীকী রূপে সমগ্র মানবজাতিকে। কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতে প্রকৃতি, প্রেম, আধ্যাত্মিকতা এবং মানবিকতার সুর মিশে আছে। সরল অথচ গভীর ভাষা, মাধুর্যমণ্ডিত ছন্দ ও আবেগঘন বর্ণনা উৎসর্গ কাব্যগ্রন্থকে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার এক অনন্য প্রকাশে পরিণত করেছে।
৫ খেয়া
খেয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ, যা ১৯০৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে কবি জীবনের যাত্রা, মৃত্যু ও অমরত্বের দর্শন, প্রেম, মানবতা এবং আত্মোপলব্ধির গভীর চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন। খেয়া নামটি প্রতীকী—এটি জীবনের পারাপার, অনিত্যতা ও গন্তব্যে পৌঁছানোর যাত্রাকে বোঝায়। গ্রন্থের কবিতাগুলিতে দার্শনিক ভাবনা, আধ্যাত্মিকতার অনুরণন এবং প্রকৃতির বর্ণনা মিলেমিশে এক অনন্য আবহ তৈরি করেছে। ভাষা মাধুর্যময়, ছন্দ সুমিত এবং ভাবগভীরতা পাঠককে বারবার ভাবায়। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক কবিসত্তার উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে খেয়া বাংলা সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে।
৬ গীতাঞ্জলি
গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক অনন্য কাব্যগ্রন্থ, যা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে (বাংলা সংস্করণ) এবং পরবর্তীতে ১৯১২ সালে ইংরেজি অনুবাদে Gitanjali: Song Offerings নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি মূলত ভক্তিমূলক ও আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন, যেখানে মানব ও ঈশ্বরের মধ্যে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্কের প্রকাশ ঘটেছে। গীতাঞ্জলি-র ভাষা সহজ, গীতিধর্মী এবং গভীর আবেগপূর্ণ, যা পাঠককে আত্মার শান্তি ও অনন্ত সৌন্দর্যের সন্ধান দেয়। ১৯১৩ সালে এই গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন, যা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য এক ঐতিহাসিক মাইলফলক।
৭ গীতিমাল্য
গীতিমাল্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রভাবশালী কাব্যগ্রন্থ, যা ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত কবিতাগুলি মূলত গীতিধর্মী, যেখানে প্রেম, ভক্তি, প্রকৃতি ও মানবজীবনের সৌন্দর্য মাধুর্যময়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গীতিমাল্য-এর কবিতাগুলিতে সুর ও ছন্দের এক অনন্য সমন্বয় রয়েছে, যা গান হিসেবেও জনপ্রিয় হয়েছে। এখানে রবীন্দ্রনাথের ভক্তিমূলক ও আধ্যাত্মিক ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক আবেগের গভীরতা ফুটে উঠেছে। ভাষা সহজ, সুরেলা এবং হৃদয়গ্রাহী, যা পাঠক ও শ্রোতার মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে। বাংলা গীতিকাব্যের ধারায় গীতিমাল্য একটি অমূল্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হয়।
৮ গীতালি
গীতালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ, যা ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি মূলত গীতিধর্মী, যেখানে প্রেম, প্রকৃতি, ভক্তি এবং মানবতার সুর মিলেমিশে এক অনন্য আবহ তৈরি করেছে। গীতালি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষা আরও পরিশীলিত ও সুরম্য হয়ে ওঠে, যেখানে সুর ও ছন্দের সঙ্গে ভাবের গভীরতা সুন্দরভাবে মিশে গেছে। এতে জীবনের আনন্দ, প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভালোবাসা বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি পরবর্তীতে বহু রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল পাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যা বাংলা গানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।
৯ বলাকা
বলাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অনন্য কাব্যগ্রন্থ, যা ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী অস্থির সময়ে রচিত হলেও, এতে কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে গতি, পরিবর্তন ও জীবনের অনন্ত প্রবাহের দিকে। বলাকা নামটি এসেছে আকাশে উড়ন্ত রাজহাঁসের দল থেকে, যা এখানে গতি ও মুক্তির প্রতীক। গ্রন্থের কবিতাগুলিতে প্রকৃতি, মানবজীবন এবং মহাবিশ্বের এক অপার চলমানতার চিত্র ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ এতে একদিকে ব্যক্তিগত অনুভূতি, অন্যদিকে বিশ্বমানবতার প্রতি তার ভাবনা মিলিয়ে এক নতুন কাব্যধারা উপস্থাপন করেছেন। ছন্দ, শব্দসৌন্দর্য ও ভাবের গভীরতা এই গ্রন্থকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।
১০ পলাতকা
পলাতকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কাব্যগ্রন্থ, যা ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়। এটি মূলত গল্পকবিতার আকারে রচিত, যেখানে নারীজীবনের সমসাময়িক সমস্যা, সংগ্রাম এবং আবেগকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপটে রচিত এই গ্রন্থে নারীর অন্তর্গত অনুভূতি, বেদনা ও প্রতিবাদের সুর স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। পলাতকা শিরোনামটি প্রতীকী অর্থে ব্যবহার হয়েছে—যা মুক্তি, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও সামাজিক বাঁধন থেকে পালানোর মানসিকতাকে ইঙ্গিত করে। ভাষার সরলতা, ছন্দের মাধুর্য এবং মানবিক সহানুভূতির গভীর প্রকাশ এই কাব্যগ্রন্থকে রবীন্দ্রনাথের সামাজিক ভাবনার অন্যতম নিদর্শন করে তুলেছে।
১১ শিশু ভোলানাথ
শিশু ভোলানাথ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিশুতোষ কাব্যগ্রন্থ, যা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। এটি মূলত শিশুদের জন্য লেখা হলেও এর কাব্যিক সৌন্দর্য প্রাপ্তবয়স্ক পাঠককেও সমানভাবে মুগ্ধ করে। গ্রন্থটির কেন্দ্রে রয়েছে এক চঞ্চল, নির্ভীক ও কৌতূহলী শিশু চরিত্র—ভোলানাথ, যার চোখে দেখা প্রকৃতি, মানুষের আচরণ এবং গ্রামীণ জীবনের রঙিন ছবি কবিতায় প্রাণ পেয়েছে। শিশু ভোলানাথ শুধু একটি শিশু-কবিতার সংকলন নয়, বরং শৈশবের আনন্দ, স্বাধীনতা এবং কল্পনার এক শিল্পসম্মত প্রকাশ। ভাষা সহজ, ছন্দ মধুর ও চিত্রকল্প জীবন্ত, যা বাংলা শিশু সাহিত্যে এই কাব্যগ্রন্থকে এক অনন্য উচ্চতায় স্থান দিয়েছে।
১২ পূরবী
১৩ লেখন
লেখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কাব্যগ্রন্থ, যা তাঁর সাহিত্যকর্মে এক অনন্য সংযোজন হিসেবে গণ্য হয়। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মূলত আত্মজিজ্ঞাসা, সৃজনশীলতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং শিল্পীর মানসিক দ্বন্দ্বকে কাব্যিকভাবে ব্যক্ত করেছেন। লেখন-এর কবিতাগুলিতে লেখকের আত্মপ্রকাশ এবং সৃষ্টিশীলতার আনন্দ ও বেদনা সমানভাবে ধরা পড়েছে। এখানে কলম কেবল লেখার যন্ত্র নয়, বরং ভাবনার সেতু, যা কবির অন্তর্জগতকে বহির্জগতের সঙ্গে যুক্ত করে। ভাষা সহজ হলেও ভাবগভীরতা প্রবল, এবং চিত্রকল্পে রয়েছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সর্বজনীন সত্যের মেলবন্ধন। ফলে লেখন বাংলা সাহিত্যে কবিতার নন্দনতত্ত্বে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে।
১৪ মহুয়া
মহুয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৯২৯ সালে প্রকাশিত একটি কাব্যগ্রন্থ, যা মূলত প্রেম, প্রকৃতি ও মানবমনের গভীর অনুভূতির কাব্যিক প্রকাশ। এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে কবি গ্রামীণ জীবনের সরলতা, ফুল-ফল-গাছপালার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং প্রেমের নিবিড় আবেগকে চিত্রিত করেছেন। মহুয়া নামটি নিজেই গ্রামীণ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতীক, যা কবিতাগুলিতে বারবার রূপক ও প্রতীক হিসেবে এসেছে। ভাষার সৌন্দর্য, ছন্দের মাধুর্য ও চিত্রকল্পের বৈচিত্র্যে এই গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। এখানে প্রেম কেবল রোমান্টিক অর্থে নয়, বরং জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির চিরন্তন মেলবন্ধনের রূপে প্রকাশিত হয়েছে। মহুয়া বাংলা কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরিণত ভাবনার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।
শেষ পর্ব (১৯৩০ – ১৯৪১) :
১. বনবাণী ১৯৩১
২. পরিশেষ ১৯৩২
৩. পুনশ্চ ১৯৩২
৪. বিচিত্রতা ১৯৩৩
৫. শেষ সপ্তক ১৯৩৫
৬. বীথিকা ১৯৩৫
৭. পত্রপুট ( ১৯৩৬)
৮. শ্যামলী ১৯৩৬
৯. খাপছাড়া ১৯৩৭
১০. ছড়ার ছবি ১৯৩৭
১১ প্রান্তিক ১৯৩৮
১২ সেঁজুতি ১৯৩৮
১৩ প্রহাসিনী ১৯৩৮
১৪ আকাশ প্রদীপ ১৯৩৯
১৫ নবজাতক ১৯৪০
১৬ সানাই ১৯৪০
১৭ রোগশয্যায় ১৯৪০
১৮ আরোগ্য ১৯৪১
১৯ জন্মদিনে ১৯৪১
২০ শেষলেখা ১৯৪১